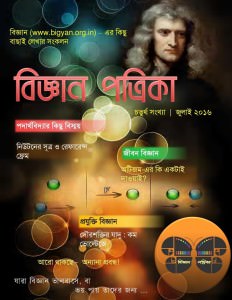21-02-2026 23:36:00 pm
বিজ্ঞান - Bigyan
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম
An online Bengali Popular Science magazine
https://bigyan.org.in
‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র চতুর্থ সংখ্যা : নিউটনের সূত্র ও অন্যান্য প্রবন্ধ
Link: https://bigyan.org.in/bigyan-patrika-4

এই ওয়েবসাইটের লেখাগুলি থেকে পাঁচটি লেখা নিয়ে আমরা প্রকাশ করতে চলেছি বিজ্ঞান পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দম-বন্ধকর চাপের মাঝে বিজ্ঞানপাঠের উৎসাহ ফিরিয়ে আনতে ‘বিজ্ঞান’-এর প্রচেষ্টা শুরু করেছিলাম আমরা। পাঠকদের কাছ থেকে যে বিপুল সাড়া পেয়েছি, তাতে আমাদের উৎসাহ আর এক নতুন মাত্রা পেয়েছে।
আগের সম্পাদকীয়গুলোতে আমরা বলেছিলাম মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার কেন প্রয়োজন, কিংবা কেন আমরা এই ‘বিজ্ঞান পত্রিকা’ শুরু করলাম। এবার প্রচলিত বিজ্ঞানশিক্ষা কেন এই প্রয়োজন সঠিকভাবে মেটাতে পারছে না, তার একটি দিকের উল্লেখ করতে চাই। আমরা জ্ঞান-উন্মেষের পর থেকেই “বিজ্ঞানের গরিমা” শুনতে শুনতে বড় হই। খুব ছোট বয়সেই অঙ্ক বা বিজ্ঞানকে বাৎসরিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের চাবিকাঠি এবং সমাজের চোখে বুদ্ধিদীপ্ততার পরিচয় হিসাবে মজ্জাগত করে ফেলি।
সূত্রগুলো পড়ার সময় আমরা খুব একটা ভেবে দেখিনা, “সূত্র বা তাদের সাথে যুক্ত ফর্মুলাগুলোর গুরুত্ব কি?”
কিন্তু, এই ধরণের ভাবনা বোধহয় বিজ্ঞান শিক্ষার পরিপন্থী। একটা উদাহরণ দিই। বিজ্ঞানের ক্লাসে আমরা হরেক “সূত্র”-এর সাথে পরিচিত হই এবং সেগুলো থেকে নানা রকমের প্রবলেম সমাধান করি, মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন করি। অনেকে বিজ্ঞানচর্চা আর বিজ্ঞানের সূত্রের ফর্মুলা জানা প্রায় সমার্থক শব্দ হিসাবেই ব্যবহার করে। এসবের মাঝে আমরা খুব একটা ভেবে দেখিনা, “সূত্র বা তাদের সাথে যুক্ত ফর্মুলাগুলোর গুরুত্ব কি?” কোন ক্ষেত্রে কোন ফর্মুলা লাগছে, বহু প্র্যাক্টিসের মাধ্যমে তার একটা আন্দাজ তৈরি করতে পারলেই যেন খেল খতম!
অথচ সূত্রগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি না করতে পারলে কিছুই বোঝা হলো না তো! মহাবিশ্বে কতশত হরেক রকমের বস্তু আছে। এদের আকৃতি ভিন্ন, রং ভিন্ন। সমস্ত বস্তুর মধ্যে যে সার্বজনীন বৈশিষ্ট থাকবে, এমন মাথার দিব্যি কেউ দেয় নি। কিন্তু তবুও জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে নানারকম সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়! এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় কি? নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের কথাই ধরা যাক। ছোট-মাঝারি-বড়ো, কঠিন-তরল-গ্যাস সবাই একই নিয়ম মেনে আকর্ষণ করছে, এটা একটা দারুণ ব্যাপার নয় কি?
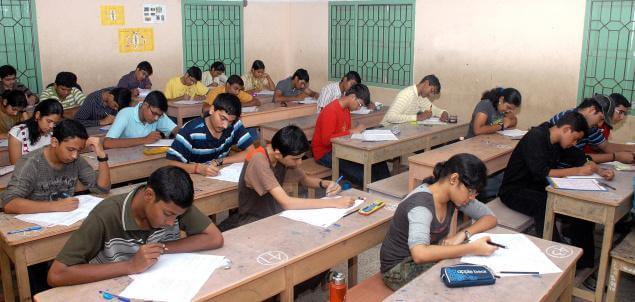
বিজ্ঞান পড়ার সময় এই বিষয়গুলি যদি ভেবে না দেখি অথবা যদি জিগ্যেস করার সুযোগ না থাকে তাহলে বিজ্ঞানচর্চা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সূত্রগুলিকে প্রশ্ন না করেই মুখস্থ করার মধ্যে কোনো মেধার পরিচয় নেই। সর্বোপরি, যেহেতু অনেক সূত্রের কোনো প্রমাণ হয়না, তাই এদের সম্ভাব্য সংশোধন বা সংযোজন নিয়ে চিন্তা ভাবনা আবশ্যক। কিন্তু চোখ বুজে সব মেনে নিলে সেসবের সুযোগ কই?
পরীক্ষায় তথ্য মুখস্থ করে নম্বর পাওয়া যায় বটে কিন্তু আজ যেখানে ইন্টারনেটের সৌজন্যে নিমেষে এই তথ্য হাতের মুঠোয় তখন এই জিনিসগুলো মুখস্থ করার মানে কী?
একই কথা বলা যায় তথ্যের ক্ষেত্রেও। পরীক্ষায় কত তথ্যমূলক প্রশ্ন আসে – পৃথিবীর থেকে সূর্যের দূরত্ব কত, ইলেক্ট্রনের ভর কত, অ্যাভোগাড্রো সংখ্যার মান কত, বৃহস্পতির ব্যাস কত, প্রোটনের আধান কত ইত্যাদি। এগুলো মুখস্থ করে নম্বর পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আজ যেখানে ইন্টারনেট, ‘গুগল’-এর সৌজন্যে নিমেষে এই তথ্য হাতের মুঠোয় তখন এই জিনিসগুলো মুখস্থ করার মানে কী? বরং আমরা প্রশ্ন করি এই তথ্যগুলো কোথা থেকে এল তা নিয়ে। কী করে মাপা হল ইলেকট্রনের ভর? এই অতিক্ষুদ্র কণার ভর যে পদ্ধতিতে মাপা হয়, সেই একই পদ্ধতিতে কি আমরা সূর্যের ভরও মাপতে পারি। কী করেই বা মাপব বিশাল কোন গ্যালাক্সির ভর? বা আলোর ভর? প্রশ্ন করতে শেখার মজা হল একবার তা শুরু হলে থামতেই চায় না!
নিউটন সাহেব প্রশ্ন করেছিলেন – আপেলটি কেন নিচে পড়লো? বর্তমানে কিছু শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে মনে হয় তিনি হয়তো কোনো দিন প্রশ্নটি করার সাহস করতেন না।
না জানা বা না বোঝা কোনোটিই বিজ্ঞানচর্চার অন্তরায় নয়। বরং নিজের অজ্ঞতাকে উপলব্ধি করা বিজ্ঞান চর্চার প্রথম ধাপ। ‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-তেও আমরা সেটাই মাথায় রেখে চলি। শুধু কিছু তথ্য পরিবেশন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা চাই পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগাতে।
এই পত্রিকায় নিউটনের গতিসূত্র ও দর্শক (observer)-এর ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী জয়ন্ত ভট্টাচার্য। বহু বছরের শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতায় তাঁর উপলব্ধি – “পদার্থ বিজ্ঞানের স্থানীয় পাঠ্যপুস্তক গুলিতে নিউটনের সূত্র (Newton’s laws) সম্বন্ধে যা প্রাণ চায় তাই লেখা থাকে। সভ্য জগতে কোথাও এটা দেখা যায় না।” ভাবনা-চিন্তা না করে বিজ্ঞানের সূত্র পড়ার যে পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমরা অনেকেই বেড়ে উঠেছি, এখনো পরীক্ষায় আসা কিছু প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় “সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে”। ‘বিজ্ঞান’-এর দুই পাঠক এমন একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। প্রশ্নটি হল – নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে তৃতীয় গতিসূত্র কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। পাঠকের দরবার বিভাগে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন প্রফেসর ভট্টাচার্য-ই। ভালো ফলাফলের তাগিদে আমরা অনেকেই নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে প্রথম সূত্র বা তৃতীয় সূত্র ‘প্রমাণ’ করেছি। ভেবে দেখিনি – যদি দ্বিতীয় সূত্র থেকে প্রথম সূত্র পাওয়াই যায়, তাহলে নিউটন আলাদা করে প্রথম সূত্রটা লিখতে গেছিলেন কেন?
পত্রিকার কলেবরের দিকে তাকিয়ে এই সংখ্যায় লেখার পরিমাণ সীমিত রাখা হল। নিউটনের সূত্রের উপর লেখাদুটো ছাড়াও পত্রিকার অন্য লেখাগুলিও প্রশ্ন থেকে শুরু হয়েছে। যেমন:
- সৌরশক্তির জাদু : কম ভোল্টেজে – সূর্যের তেজকে দৈনন্দিন জীবনে সরাসরি কিভাবে কাজে লাগানো যায়?
- বাদুড়ের বাদড়ামি – আমরা জানি বাদুড় নিজের ডাক ছেড়ে তার প্রতিধ্বনি শুনে দিক নির্ণয় করে, কিন্তু অনেকগুলো বাদুড় জুটে গেলে কে কার ডাকের প্রতিধ্বনি শুনছে সেটা বোঝে কি করে?
- অটিজম-এর কি একটাই দাওয়াই? – অটিজম একটা রোগ না শুধু অনেকগুলো আলাদা আলাদা চারিত্রিক বৈশিষ্টের সমষ্টি? কখন সেটা রোগের আওতায় আসে? রোগটা ধরেই বা কি করে আর রোগীদের চিকিৎসাই বা কি?
আশা করি সব কটি লেখা পাঠকদের খুব ভালো লাগবে। অনুরোধ রইলো চারপাশে সবার মধ্যে বিজ্ঞান পত্রিকাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।
লেখাটি অনলাইন পড়তে হলে নিচের কোডটি স্ক্যান করো।
Scan the above code to read the post online.
Link: https://bigyan.org.in/bigyan-patrika-4