পশুজগতে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হলো সাইজের বৈচিত্র্য। কিন্তু কোনো কারণে প্রাণীবিশারদরা সেই নিয়ে প্রায় মাথা ঘামাননি। আমার সামনে জু’লজি-র একটা ইয়াব্বড় পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। তাতে কোথাও ইঙ্গিত পাইনা যে ঈগল চড়াইয়ের থেকে বড় কিংবা জলহস্তী খরগোশের থেকে। খালি ইঁদুর আর তিমির কথা বলতে গিয়ে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের সাইজের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সহজেই দেখানো যায় যে জলহস্তীর সাইজের খরগোশ হতে পারতো না কি হেরিং-এর (অনুবাদক: পুঁটিমাছও ভাবা যায়) মতো পুচকে তিমি পাওয়া সম্ভব ছিল না। যে কোনো প্রজাতিরই একটা সবথেকে সুবিধের সাইজ রয়েছে, সেই সাইজ-এ বড় মাপের হেরফের হলে প্রজাতিটার গঠন-ও এক থাকবে না।
কী-হতে-পারতো-র রাজ্যে সবথেকে চেনা কেসটাকেই ধরা যাক। ষাট ফুট উচ্চতার দৈত্যাকার মানুষ — আমার ছোটবেলায় পড়া Pilgrim’s Progress বইটাতে Giant Pope কিম্বা Giant Pagan-এর মতো (অনুবাদক: এখানে ভারতীয়রা মহাভারতের ‘ঘটোৎকচ’ কিংবা চাচা চৌধুরী-র বইয়ের ‘সাবু’-কে ভাবতে পারেন)। এই দৈত্যাকৃতি মানুষেরা সাধারণ মানুষের থেকে দশ গুণ লম্বাই নয়, সামনে-পিছনে কিংবা আড়াআড়িও সেইরকমই। সবসুদ্ধ এদের ওজন তাহলে হাজারগুণ অর্থাৎ আশি নব্বই টন হবে [১]। কিন্তু ওদের হাড়ের প্রস্থচ্ছেদ একই হিসেবে সাধারণের থেকে মাত্র একশোগুণ বেশি। সব মিলিয়ে দাঁড়ায় যে ওদের হাড়ের প্রত্যেক স্কোয়ার ইঞ্চিকে সাধারণ মানুষের হাড়ের এক স্কোয়ার ইঞ্চি-র দশগুণ বেশি ভার বহন করতে হবে। মানুষের উরুর হাড়ে দশগুণ বেশি চাপ পড়লে সেটা ভেঙ্গে যায়, অর্থাৎ Pope বা Pagan (আমাদের ঘটোৎকচ বা সাবু) সত্যিই থেকে থাকলে প্রত্যেক পদক্ষেপে একবার করে তার হাড় ভাঙ্গতো। তাই বোধহয় বেশিরভাগ ছবিতেই ওদের বসে থাকতে দেখি। কিন্তু এইভাবে ভাবলে Christian বা Jack the Giant Killer-এর প্রতি শ্রদ্ধা কমে যায় (অর্থাৎ ছোট সাইজের কেউ এদের পরাস্ত করলে আশ্চর্যের কিছু নেই)।
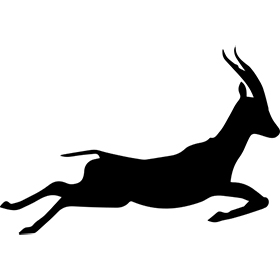
পশুবিদ্যায় ফেরা যাক। গ্যাজেল (gazelle) এক জাতীয় খুদে হরিণ, লম্বা সরু পায়ে ভর দিয়ে ছুটে বেড়ায়। হঠাৎ যদি সে আজ সাইজে বেড়ে যেত, তারও হাড়গোড় ভাঙ্গা দশা হতো, যদি না একই সাথে তার আরো একটা পরিবর্তন ঘটতো। হয় তার পা’গুলো গণ্ডারের মতো বেঁটে আর গাবদা হয়ে যেতে পারতো যাতে বেড়ে যাওয়া ওজনের অনুপাতেই হাড়ের প্রস্থচ্ছেদও বাড়ে। নয়তো দেহটাকে সংকুচিত করে ওজন কমিয়ে পা’দুটোকে তেরছা করে দাঁড়িয়ে সেই ওজন সামলাতে পারতো, খানিকটা জিরাফের মতো। এই দুটো প্রাণীর কথা বলছি কারণ একদিক দিয়ে গ্যাজেলের সমগোত্রীয় এরা। এরা সকলেই চলাফেরায় সফল, প্রয়োজনে ছুটতে পারে দ্রুতগতিতে।

দৈত্যাকার মানুষ সত্যিই থেকে থাকলে প্রত্যেক পদক্ষেপে একবার করে তার হাড় ভাঙ্গতো।
মাধ্যাকর্ষণ মানুষের কাছে শুধুমাত্র একটা বিরক্তিকর অসুবিধে মাত্র কিন্তু দৈত্যের কাছে সেটা একটা আতঙ্ক। এদিকে নেংটি ইঁদুর কিংবা তার থেকেও ছোট কোনো প্রাণীর প্রকৃতপক্ষে মাধ্যাকর্ষণকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। হাজার গজ নিচু খনিগর্ভে একটা নেংটি ইঁদুরকে ফেলে দিতে পারো। সে মাটিতে পড়ে একটু ঘাবড়ে যাবে বটে কিন্তু কিছুক্ষণেই চলতে শুরু করবে, অবশ্যই নিচের জমিটা খুব শক্ত না হলে। একটা ধেড়ে ইঁদুর একই অবস্থায় মরে যাবে, মানুষ ভেঙ্গে যাবে আর ঘোড়া থেঁতলে যাবে। কারণ পড়ার মুখে বাতাসের প্রতিরোধ পড়ন্ত প্রাণীর প্রস্থচ্ছেদের সাথে সমানুপাতিক। প্রাণীটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা প্রত্যেকটাকেই দশ দিয়ে ভাগ করো, তার ওজন হাজার ভাগের একভাগ হয়ে যাবে কিন্তু পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল হবে একশো ভাগের এক ভাগ। তাই প্রাণীটি ছোট হয়ে গেলে তার ওপর বাতাসের প্রতিরোধ কমবে একশো ভাগ কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের টান কমবে হাজার ভাগ [২]। সুতরাং ক্ষুদ্র জীবের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বাতাসের প্রতিরোধ ক্ষমতা মাধ্যাকর্ষণের তুলনায় দশ গুণ বেশি।

তাই, একটা পোকার মাধ্যাকর্ষণের থেকে কোনো শঙ্কা নেই। সে নির্ভয়ে ভূমিসাৎ হতে পারে আবার সিলিং-এ সেঁটেও থাকতে পারে অনায়াসে। সেঁটে থাকার জন্য মাকড়শার পায়ের মতো নিপুণ কারুশিল্পেরও আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু আরেকটা বল আছে যেটার কাছে তারা ধরাশায়ী হয়। সেটা হলো পৃষ্ঠটান (surface tension)। স্নান সেরে বেরোনোর সময় মানুষের দেহের উপর এক ইঞ্চির পঞ্চাশভাগ পুরু একটা জলের স্তর থাকে। পুরো স্তরটার ওজন করলে এক পাউন্ডও হবে না। একটা জলসিক্ত ইঁদুরকে তার ওজনের সমান জল বইতে হয়। একটা মাছির ক্ষেত্রে সেই ওজনটাই হয়ে যায় নিজ ওজনের বহুগুণ [৩]। জানোই তো, একটা মাছিকে একবার জলে কিংবা অন্য কোনো তরলে ফেলে দিলে সে মহা বেকায়দায় পড়ে যায়। একটা পতঙ্গের জল খেতে যাওয়া আর একজন মানুষের খাদের কিনারায় ঝুঁকে খাবারের খোঁজ করা একইরকম বিপজ্জনক। পতঙ্গ একবার জলের পৃষ্টটানের কবলে পড়লে, অর্থাৎ একবার ভিজলে, সেই জলেই আটকা পড়বে যতক্ষণ না সে ডুবে যাচ্ছে। কিছু পোকা আছে যাদের ভেজানো যায়না, যেমন ওয়াটার-বীটল (water-beetle)। কিন্তু অধিকাংশই চেষ্টা করে জলের থেকে বহুদূরে থেকে শুঁড়ের মাধ্যমে পিপাসা মেটাতে।
একটা পোকার মাধ্যাকর্ষণের থেকে কোনো শঙ্কা নেই কারণ তার ক্ষেত্রে বাতাসের প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি।
লম্বা হওয়ার আবার অন্য হ্যাপা রয়েছে। লম্বা স্থলচর প্রাণীদের দেহে রক্ত চলাচল বজায় রাখতে মানুষের থেকে বেশি উচ্চতায় রক্ত পাম্প করতে হয়। তাই রক্তচাপও বেশি, রক্তনালীগুলোকেও সেই চাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাখতে হয়। বেশ কিছু মানুষের ধমনী ফেটে মারা যাওয়ার কথা আমরা শুনেছি, কিন্তু জিরাফ বা হাতির ক্ষেত্রে সেই সংখ্যাটা আরো বেশি। তবে আয়তন নির্বিশেষে সব পশুকেই একটা সমস্যার সমাধান করতে হয়। ধরো একটা ক্রিমি বা rotifer-জাতীয় কীট। তার চামড়া হয় মসৃণ যাতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন শুষে নিতে পারে, তার খাদ্যনালী হয় একটি সিধা গহ্বর যার গায়ে খাদ্য শোষণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকে, আবর্জনা ত্যাগ করার জন্য থাকে একটিমাত্র কিডনি। এই কীটেরই মাপ সবদিকে দশগুণ বাড়িয়ে দাও। ওর ওজন বেড়ে যাবে হাজারগুণ, ফলে মাংসপেশীগুলোকে একইরকম কার্যকর হতে গেলে হাজারগুণ খাদ্য ও অক্সিজেন শোষণ করতে হবে, ত্যাগও করতে হবে সেই পরিমাণ বর্জ্য পদার্থ।

এবার সেই কীটের গঠন যদি একইরকম থাকে, তার উপরিতল বাড়বে মাত্র একশোগুণ। অর্থাৎ বৃহদকায় কীটটির চাহিদা মেটাতে দেহের প্রত্যেক স্কোয়ার মিলিমিটার-এ দশগুণ বেশি অক্সিজেন প্রবেশ করতে হবে। একইভাবে অন্ত্রের প্রত্যেক স্কোয়ার মিলিমিটার-এ দশগুণ খাদ্য শোষণের প্রয়োজন হবে। শোষণক্ষমতা সীমায় এসে ঠেকলে তখন অন্য উপায়ে এদের শোষণতলটাকে বাড়ানোর ফন্দি করতে হবে। চামড়ার একটা অংশ ঝুড়ি ঝুড়ি চুলের মতো বেরিয়ে আসতে পারে, যেমন মাছের কানকোতে থাকে, কিংবা ভিতরে সেঁদিয়ে যেতে পারে, যেমন মানুষের শ্বাসযন্ত্রে হয়। মানুষের শ্বাসযন্ত্রে প্রায় একশো স্কোয়ার গজ শোষণতল আছে। একইভাবে, খাদ্যনালী সিধা না হয়ে পাকিয়ে যায়, উপরিতলটা মসৃণের পরিবর্তে হয়ে যায় মখমলের মতো। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও জটিলতা দেখা যায়। প্রাণীজগতের উপরের দিকের বাসিন্দারা আয়তনে বড় এই কারণে নয় যে তারা বেশি জটিল। তারা বেশি জটিল এই কারণে যে তাদের আয়তন বড়। একই যুক্তি উদ্ভিদদের ক্ষেত্রেও খাটে। সরলতম উদ্ভিদগুলো, যেমন ডোবার স্থির জলে বা গাছের ছালে জমা শ্যাওলা (algae), শুধু গোলাকার কোষ মাত্র। এর থেকে উপরের শ্রেণীর উদ্ভিদরা চেষ্টা করে পাতা কিংবা শিকড় মেলে নিজেদের শোষণতল বাড়াতে।
শেষপর্যন্ত গঠনবিষয়ক তুলনামূলক আলোচনা উপরিতল বনাম আয়তনের লড়াইয়ে এসে ঠেকে [৪]। উপরিতল বাড়ানোর কিছু পদ্ধতি খানিকদূর পর আর কাজ করে না। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা রক্তের মাধ্যমে ফুসফুস থেকে দেহের সর্বত্র অক্সিজেন চালান করে। কীটপতঙ্গের দেহে কিন্তু অক্সিজেন পরিবহন সরাসরি কিছু নলের মাধ্যমে হয়, যাদের বলে tracheae। এই নলগুলো দেহের বিভিন্ন জায়গায় হাঁ করে বাইরে থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। শ্বাস নেওয়ার সময় অক্সিজেন সরাসরি গৃহীত হলেও সেই অক্সিজেনকে নলের সূক্ষ্মতর শাখাগুলোতে diffusion বা আশ্লেষের মাধ্যমে ছড়াতে হয়। যে কোনো গ্যাস অল্প দূরত্বে সহজেই ছড়াতে পারে। তবে এই দূরত্বটা খুব বেশি নয়, গ্যাসীয় অণুর সংঘর্ষের মাঝে যাত্রাপথের যে গড় দূরত্ব, তার কয়েকগুণ মাত্র। কিন্তু একটা অণুকে যদি এক ইঞ্চির চতুর্থাংশের মতো মহাযাত্রায় বেরোতে হয়, তখন এই পরিবহনপদ্ধতি অত্যন্ত ঢিমে চালায় এগোয়। ফলে একটা পোকার দেহের যেসব অংশ খোলসের থেকে এক চতুর্থাংশ ইঞ্চির বেশি ভিতরে থাকবে, তারা সবসময়ই অক্সিজেনের খরায় ভুগবে [৫]। অতএব ওই সাইজের থেকে পুরুষ্ঠু পোকা দেখা যায়না। কাঁকড়ার মতো পুরুষ্ঠু প্রাণীও হয় যাদের দেহের মানচিত্রটা কিছুটা পোকা গোত্রেই। কিন্তু কাঁকড়াও রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন চালান করে তবেই সাধারণ কীটপতঙ্গের থেকে অনেক বড় আয়তনে পৌঁছতে পেরেছে। কীটপতঙ্গরাও যদি তাদের কলা-র (tissue) মধ্যে দিয়ে বাতাসটাকে নিজ মর্জিতে চলতে না দিয়ে জোর খাটিয়ে পরিচালনা করতে পারতো তাহলে অন্তত তাদের গলদা চিংড়ির সাইজে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যদিও অন্য নানাবিধ কারণে তখনও হয়তো তারা মানুষের সাইজে পৌঁছতে পারতো না।
বাতাস শোষণক্ষমতা সীমায় এসে ঠেকলে তখন অন্য উপায়ে শোষণতল বাড়াতে হয়, যেমন মাছের কানকো কিম্বা মানুষের শ্বাসযন্ত্র।

একই সমস্যা ওড়ার ক্ষেত্রেও। বিমানচালনাবিদ্যার একটা গোড়ার সূত্র হলো এইটে: একটা বিমানের আকৃতি একই রাখলে, তাকে ভাসমান থাকতে ন্যূনতম যে গতি বজায় রাখতে হবে সেটা তার দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সমানুপাতিক। অর্থাৎ বিমান চারগুণ লম্বা হলে তাকে ভাসমান থাকতে দ্বিগুণ গতিতে চলতে হবে। এর থেকে দাঁড়ায় যে একটা বিমানকে ভাসমান রাখতে যে ক্ষমতার (power) প্রয়োজন সেটা বিমানের আয়তন বাড়ালে ওজনের থেকে দ্রুতগতিতে বাড়ে। একটা জাম্বো বিমান, যেটা একটা ছোট বিমানের থেকে চৌষট্টিগুণ ভারী (সবদিকেই চারগুণ বাড়ালে) ভাসমান থাকতে দুশো ছাপ্পান্নগুণ ক্ষমতা দাবী করবে [৬]। একই তত্ত্ব পাখিদের ওপর প্রয়োগ করলে খুব শীঘ্রই তাদের আয়তন সম্ভবের সীমা ছাড়িয়ে যাবে। যদি পরীরা বাস্তবে থাকতো আর ঈগল বা পায়রার মতোই ওজনের সাথে সাথে তাদের ক্ষমতার খাঁই বাড়তো, তাহলে তাদের চার ফুট গভীর বুকের পেশী লাগতো ডানা ঝাপ্টে ভাসমান থাকতে। একই সাথে ওজনের ভার কমাতে পা’গুলো হয়তো প্যাঁকাটির মতো হয়ে যেত। যদি খেয়াল করো, ঈগল বা চিলের মতো বড় পাখী কিন্তু ডানা ঝাপটে ভেসে থাকে না। বেশিরভাগ সময় তারা স্রেফ ডানা মেলে একটা উর্ধ্বগামী বাতাসের থামের উপর নিজেদের ব্যালান্স করে। তবে সেটাও আয়তন বাড়ার সাথে সাথে অসম্ভবের দিকে পাড়ি দেয়। তা না হলে বাঘের সাইজের ঈগল উড়ে বেড়াতো আর শত্রু বিমানের মতোই মানুষকে নাকাল করে ছাড়তো।
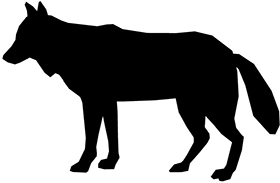
এতক্ষণ সাইজের অসুবিধে নিয়ে কথা হচ্ছিলো, এবার সুবিধেগুলো বলি। সবথেকে প্রকট যে সুবিধেটা সেটা হলো দেহের উষ্ণতা বজায় রাখা। সব উষ্ণ রক্তের জীবই স্থির অবস্থায় দেহের এক একক ক্ষেত্র থেকে একই পরিমাণ তাপ হারায়। এই হারানো শক্তি পূরণ করতে তাদের যে খাদ্যভাণ্ডারের প্রয়োজন হয় সেটা তাদের উপরিতলের সাথে সমানুপাতিক, গোটা ওজনের সাথে নয়। পাঁচ হাজার নেংটি ইঁদুর মিলে তবে একটা মানুষের ওজনের সমান হয়। কিন্তু তাদের সম্মিলিত উপরিতল এবং ফলে খাদ্য বা অক্সিজেনের প্রয়োজন মানুষের সতেরোগুণ। একটা নেংটি ইঁদুর রোজ তার ওজনের এক চতুর্থাংশ ভক্ষণ করে, যার বেশিরভাগটাই তার দেহের উষ্ণতা বজায় রাখার পিছনে চলে যায়। একই কারণে শীতপ্রধান দেশগুলোতে ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী বিরল। স্পিৎজবার্গেন শহরে সবথেকে ছোট জন্তু হলো শেয়াল। শীতকালে ছোট পাখীরা পরিযায়ী হয়ে পালিয়ে যায় এবং কীটপতঙ্গ মরে যায়, যদিও তাদের ডিমগুলো ছ’মাস বা তার বেশি তুষার সহ্য করতে পারে। এইরকম পরিবেশে সবথেকে সফল প্রাণী ভল্লুক, সীল ও সিন্ধুঘোটক।

আয়তনের তুলনায় ক্ষেত্রফল কম হওয়ার সুবিধেও আছে: হারানো শক্তি পূরণ করতে খেতে হয় কম।
একইভাবে, চোখ ইন্দ্রিয় হিসেবে বেশ অকেজো যতক্ষণ না তার সাইজ একটা মাত্রা ছাড়াচ্ছে। চোখের পিছনদিকের পর্দা, যেখানে বহির্জগতের ছবি ধরা পড়ে, একটা ক্যামেরা-র ফিল্মের মতো। এই পর্দা আদতে ‘রড আর কোন’ কোষের এক মোজাইক, যেখানে একেকটা কোষের ব্যাস আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের থেকে কিঞ্চিৎ বেশি। একটা চোখে এরকম পাঁচ লক্ষ মতো কোষ রয়েছে। দুটো বস্তুকে আলাদা করতে হলে তাদের প্রতিবিম্বগুলোকে আলাদা রড কিংবা কোন-এর মধ্যে তৈরি হতে হবে। অর্থাৎ, আমাদের চোখের রড এবং কোন কোষ সংখ্যায় কম কিন্তু সাইজে বড় হলে আমাদের দৃষ্টিশক্তি আরো আবছা হয়ে যেত। তারা দ্বিগুণ বড় হলে দুটো বস্তুকে দ্বিগুণ দূরে থাকতে হতো আলাদা করে সনাক্ত করার জন্য। কিন্তু উল্টোটা সত্যি নয়। তাদের সাইজ আরো ছোট করে সংখ্যায় বাড়িয়ে দিলে কোনো লাভই হতো না। কারণ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের থেকে কম ফারাক নির্ণয় করা অসম্ভব। তাই একটা নেংটি ইঁদুরের চোখ কিন্তু মানুষের চোখের সংকুচিত মডেল নয়। অর্থাৎ তাদের রড আর কোন-গুলো সাইজে আমাদের থেকে ছোট নয়, ফলে জায়গায় কুলোতে তাদের সংখ্যা অনেক কম। একটা ইঁদুর ছ’ফুট দূরে দুটো মানুষকে আলাদা করে চিনতে পারেনা। চোখদুটো আদৌ কোনো কাজে আসতে গেলে যে সাইজের হওয়া প্রয়োজন, সেটা একটা ছোটখাটো প্রাণীর দেহের তুলনায় বেশ বড়। অন্যদিকে বড় জন্তুদের তুলনামূলকভাবে ছোট চোখেই কাজ চলে যায়। হাতি কিংবা তিমির চোখ আমাদের চোখের তুলনায় সামান্যই বড়। একই সূত্র মস্তিষ্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যদিও তার ব্যাখ্যাটা আরেকটু জটিল। যদি বিড়াল, চিতা, বাঘ, এরকম একই জাতির প্রাণীদের মস্তিষ্কের ওজনের তুলনা করি তাহলে দেখবো যে দেহের ওজন চারগুণ করে দিলে মস্তিষ্কের ওজন দ্বিগুণ বাড়ে। বড় জন্তু, তার সেইরকম বড় দেহের কাঠামো, কিন্তু চোখ, মস্তিষ্ক এবং কিছু বিশেষ অঙ্গে তারা কার্পণ্য করে থাকে।
এইরকমই কিছু ভাবনাচিন্তা থেকে দেখা যায় যে প্রাণীমাত্রেই একটা যুৎসই সাইজ আছে। যদিও গ্যালিলিও তিনশো বছর আগে বিপরীতটাই প্রমাণ করেছিলেন, অনেকের এখনো এই ধারণা আছে যে একটা মানুষের সাইজের মাছি হাজার ফুট উঁচু লাফ দিতে পারবে। একটা প্রাণী কত উঁচুতে লাফ দিতে পারবে তাকে সাইজের সমানুপাতিক বলার থেকে সাইজের ওপর নির্ভরশীল নয় বললেই বেশি সঠিক হবে। একটা মাছি দু’ফুট অব্দি যেতে পারে, মানুষ পাঁচ। বাতাসের প্রতিরোধ বাদ দিলে একটা বিশেষ উচ্চতা অব্দি লাফাতে শক্তি খরচ লম্ফমান ব্যক্তির ওজনের সমানুপাতিক। কিন্তু যদি প্রাণীনির্বিশেষে দেহের ওজনের একই ভগ্নাংশের মাংসপেশী লাফ দেওয়ার পেছনে কাজে লাগে, তাহলে প্রত্যেক আউন্স পেশীতে যে শক্তি খরচ হয়, সেটা প্রাণীর সাইজের ওপর নির্ভর করে না [৭]। অবশ্যই খরচ করতে হলে চটজলদি অতটা শক্তি সৃষ্টি করতে হবে। সেটা সবসময় সত্যি হয়না। একটা পতঙ্গের পেশী, যদিও আমাদের থেকে দ্রুততর সংকোচনে সক্ষম, আমাদের তুলনায় শক্তি রূপান্তরে ঢের বেশি অপচয়প্রবণ। নইলে একটা মাছি বা ফড়িংও লাফিয়ে ছ’ফুট অব্দি উঠতে পারতো।
একটা প্রাণী কত উঁচুতে লাফ দিতে পারবে, সেটা তার সাইজের উপর ঠিক নির্ভর করে না।
সব প্রাণীর যেমন একটা উপযুক্ত সাইজ রয়েছে, সব প্রতিষ্ঠানেরও তাই। গ্রিক ধারার গণতন্ত্রে, নাগরিকরা একরাশ বক্তৃতা শুনে বিভিন্ন আইনের প্রশ্নে সরাসরি ভোট দিতে পারতো। তাই তাদের দার্শনিকদের মতে, একটা ছোট শহরের থেকে সাইজে বড় গণতন্ত্র হতেই পারেনা। ইংরেজদের সৃষ্ট নির্বাচনী রাজনীতির ফলে একটা গোটা দেশকে গণতন্ত্রের আওতায় আনার কথা ভাবা গেল, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমে ও পরবর্তীকালে অন্যত্র তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা গেল। তারপর রেডিও সম্প্রচারের ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আবার জনগণের কাছে তাদের বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হলো, এবং কে জানে ভবিষ্যতে আবার হয়তো গ্রিক ধাঁচের গণতন্ত্রে ফেরত যাওয়া যাবে। এমনকি, রেফারেন্ডাম বা গণভোটের ধারাটাও ভাবা গেছে শুধুমাত্র দৈনিক সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে।
এক জীববিজ্ঞানীর কাছে সমাজতন্ত্র বা সোশ্যালিজম-এর সমস্যাটা বেশিরভাগটাই বেমানান সাইজের সমস্যা। কট্টর সাম্যবাদীরা সব দেশকেই একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মতো পরিচালনা করতে চান। আমার মনে হয়না হেনরি ফোর্ড-এর অ্যানডোরা কিংবা লুক্সেমবুর্গ-এর মতো ছোট দেশ চালাতে কোনো অসুবিধে হতো। এখনই ওনার কর্মচারীর তালিকা এই দেশগুলোর জনসংখ্যার থেকে বেশি। এটাও ভাবা যেতে পারে যে একদল ফোর্ড-এর মতো নেতা পাওয়া গেলে তারা হয়তো বেলজিয়াম লিমিটেড কিংবা ডেনমার্ক কর্পোরেশন-এর সংস্থাকে সামলাতে পারতো। কিন্তু একেবারে বড় দেশগুলোতে যদিও কিছু শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ স্বাভাবিক, গোটা দেশটাকেই সেই নীতিতে চালানোর কথা ভাবতে পারিনা। আমার কাছে একটা সম্পূর্ণরূপে সমাজতান্ত্রিক ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কল্পনা করা একটা ডিগবাজি খাওয়া হাতি কিংবা বেড়া টপকানো জলহস্তী কল্পনা করার থেকে কোনোভাবে সহজ নয়।
(লেখাটি মূল ইংরাজি রচনা On Being the Right Size থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছে ‘বিজ্ঞান’ টীম-এর অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা-র পাঠক সন্দীপ রায়-কে ধন্যবাদ জানাই এই অনবদ্য লেখাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।)

(ছবি: সূর্যকান্ত শাসমল)
(অন্যান্য ছবি: Freepik, সহযোগিতায়: অনির্বাণ ঘোষ)
টীকা:
[১] ধরো, একটা কিউব বা ঘনক্ষেত্র, যার প্রতিটি ধারের মাপ L, সুতরাং কিউবটার আয়তন L৩। এবার যদি প্রতিটা ধারকে ১০ গুণ বড় করে দাও, তার আয়তন বেড়ে হবে (১০L)৩ = ১০০০L৩, অর্থাৎ আগের মাপের ১০০০ গুণ। এবার দেখা যাক কিউব-টার প্রস্থচ্ছেদে বা পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলে কী ধরণের পরিবর্তন হয়। একটি কিউবে থাকে ছ’টা তল, আর প্রত্যেকটার ক্ষেত্রফল L২, অতএব সমগ্র পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল ৬L২ । কিন্তু যখন প্রতিটা ধারের দৈর্ঘ্য ১০গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হলো, তখন তার সমগ্র পৃষ্ঠতলের সমষ্টি হলো ৬ X (১০L)২ = ৬০০L২ , অর্থাৎ আগের ক্ষেত্রফলের ১০০ গুণ। প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে।
[২] পড়ন্ত বস্তুর ওপর বাতাসের প্রতিরোধ বস্তুটির ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক আর মাধ্যাকর্ষণ টান আয়তনের (বা ভরের) সমানুপাতিক।
[৩] গায়ে কতটা জল জমলো, সেটা একটা প্রাণীর উন্মুক্ত দেহের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে। প্রাণী যত ছোট হতে থাকে, তার ওজন আর সেই ক্ষেত্রফলটা একই হারে কমেনা। ক্ষেত্রফল আর ওজনের অনুপাত যেহেতু ১/L, যেখানে L হলো প্রাণীটির একদিকের মাপ, প্রাণীটা যত ছোট হবে তার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল আর ওজনের অনুপাত বাড়তে থাকবে। তাই মানুষের কাছে যেখানে জলের স্তরের ওজন নিজের ওজনের তুলনায় প্রায় নামমাত্র, মাছির কাছে সেটাই ওজনের বহুগুণ হয়ে যায়।
[৪] আমরা দেখেছি যে আয়তন এক রেখে যদি আমরা কোনো বস্তুকে ছোট ছোট টুকরো করি, তাহলে সম্মিলিত পৃষ্ঠতল বাড়তে থাকে। একটা খেলা খেলা যাক। ধরা যাক, আমাদের কাছে একটা চিনির কিউব আছে যার প্রত্যেকটি ধারের দৈর্ঘ্য ১ cm = ১০-২ m। সুতরাং চিনির কিউব-এর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল ৬ X ১০-৪ m২ । এখন ধরো, আমরা এই চিনির কিউবটাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করলাম (একটুও না খেয়ে, বিজ্ঞানের দিব্যি) এবং প্রতিটি চিনির দানা হলো ১০০ মাইক্রন = ১০-৪ m ধারের একটা কিউব। তখন সব চিনির দানাগুলোর সম্মিলিত পৃষ্ঠতল দাঁড়াবে শুরুর গোটা চিনির কিউব-এর পৃষ্ঠতলের ১০০ গুণ (খেয়াল রেখো যে এক একটা দানার ক্ষেত্রফল কম হলেও, যতগুলো দানা তৈরী হয়েছে, সেই সংখ্যাটা দিয়ে একেকটা দানার ক্ষেত্রফলকে গুণ করে তবেই সম্মিলিত পৃষ্ঠতলটা পাবে)। একইভাবে আমরা যদি ১০-৯ বা ১ ন্যানোমিটার ধারের চিনির দানাতে ভাঙ্গতাম, তাহলে ১০৭ গুণ পৃষ্ঠতল পেতাম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভর এক রেখে যখন বস্তুকে ভেঙ্গে ছোট ছোট করা হয়, সবকটা বস্তুর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল যোগ করলে যেটা হয়, সেটা বস্তুর বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যের ব্যাস্তানুপাতিকে (inversely proportional to the characteristic length) বাড়তে থাকে। এই লেখাটাতে কিছু নমুনা দেওয়া হলো যেখানে প্রকৃতি এই বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করে। কিন্তু শুধু প্রকৃতি নয়, আধুনিক বিজ্ঞানও এই ধর্মের ব্যবহার করে ন্যানোটেকনোলজিতে। আমরা যদি এক টুকরো কার্বন নিই, তার যা পৃষ্ঠতল আছে, সেটাকে ভেঙ্গে যদি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ন্যানো পার্টিকল করে ফেলি, বুঝতেই পারছো সেই তুলনায় অনেক বেশি পৃষ্ঠতল তৈরী করতে পারি। আর যে সমস্ত ক্ষেত্রে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল গুরুত্বপূর্ণ, যেমন সুপার ক্যাপাসিটরে চার্জ সংরক্ষণ (যেখানে বেশি পৃষ্ঠতল মানেই বেশি ইলেক্ট্রনের বসার জায়গা) বা তাপ পরিবহন ইত্যাদি, সেখানেও এই ধর্ম কাজে লাগানো যায়। বুঝতেই পারছো, বিবর্তন থেকে ন্যানোটেকনোলজি, সর্বত্রই সাইজ বা লেংথ স্কেল কতটা গুরত্বপূর্ণ।
[৫] হিসেবটা যাকে বলে অ্যাপ্রক্সিমেট (মোটামুটি হিসেব)। অর্থাৎ, এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে খোলসের ভিতর অক্সিজেন প্রবেশ করা মাত্রই তাকে ডিফিউশন বা আশ্লেষের মাধ্যমে বাকিটা যেতে হয়। সেই যাত্রাপথটা খুব বেশি হতে পারে না, তাই পোকারাও খুব বেশি পুরুষ্ঠু হতে পারেনা।
[৬] মূল লেখাতে ‘একশো আঠাশ গুণ’ বলা আছে। তবে, হিসেবটা যদি এইভাবে করা হয় যে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা যদি চার গুণ বাড়ে, তাহলে ওজন বাড়ে চৌষট্টিগুণ, নূন্যতম গতিবেগ (যেটা লেখা অনুযায়ী দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সাথে সমানুপাতিক) বাড়ে দ্বিগুণ, এবং সবশেষে প্রয়োজনীয় গতিশক্তি (কাইনেটিক এনার্জি) বাড়ে ৬৪ ⨉ ৪ = ২৫৬ গুণ।
[৭] যে শক্তি প্রয়োজন একটা উচ্চতা অব্দি লাফাতে, সেটা ওজনের সমানুপাতিক। আমরা জানি, স্থিতিশক্তি বা পোটেনশিয়াল এনার্জি ওজন (W) এবং উচ্চতার (h) গুণফল, অর্থাৎ W ⨉ h। তাহলে প্রত্যেক একক ওজনে যতটা শক্তি খরচ হয়, সেটা আর ওজনের ওপর নির্ভর করেনা, অর্থাৎ সব প্রাণীর ক্ষেত্রেই সমান। এবার পুরো শরীরের পেশী তো এই লাফ দেওয়ার পেছনে লাগে না। ধরে নেওয়া যাক, ওজনের একটা বিশেষ ভগ্নাংশ (f) লাফ দেওয়ার পেছনে শক্তি যোগান দেয় এবং এই ভগ্নাংশটা সব প্রাণীর ক্ষেত্রেই সমান। তাহলে একই উচ্চতা লাফাতে সব প্রাণীরই প্রত্যেক একক ওজনের পেশীতে একই পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, সব প্রাণীই একই উচ্চতা লাফাতে পারতো যদি সেই শক্তি তারা তৈরী করতে পারতো।


asadharon