নিচের পোস্ট-টা মলিকুলার জেনেটিক্স গবেষক বেনি শিলো-র লেখা ‘Life’s Blueprint’ বইটার প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ। বইটা সম্বন্ধে আরো জানতে ভূমিকাটি দেখুন।
শুরু করছি আমার নিজের জীবনের একটা গল্প দিয়ে, কিভাবে গবেষণার জগতে যাত্রা শুরু করেছিলাম, সেই গল্প। এই যাত্রায় একরাশ আবিষ্কারের সাক্ষী হতে পেরে এবং নিজেও কিছুটা অবদান রাখতে পেরে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান বলে মনে করি। এইসব আবিষ্কারের ফলেই ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধি সম্বন্ধে আজ আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা তৈরী হয়েছে। গল্পের সালটা ১৯৮১, আমি তখন ঊনত্রিশ বছর বয়েসী এক পোস্টডক্টরাল গবেষক। ম্যাসাচুসেটস-এর কেমব্রিজ শহরে MIT সেন্টার ফর ক্যান্সার রিসার্চ-এ রবার্ট এ. ওয়াইনবার্গ-এর গবেষণাগারে কাজ করছি। সেসময় এই গবেষণাগার নাম করেছিল নানারকম টিউমার থেকে ক্যান্সার-এর জন্য দায়ী জিন-কে সনাক্ত করে তাকে আলাদা করতে পেরে। এই ধরণের জিন-কে বলে অংকজিন (oncogene)। যে দল এই কাজটা করেছিল, তার একজন সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।
আমাদের এই আবিষ্কার হঠাৎ করে হয়নি। এর আগে বেশ কিছু ল্যাব-এ আরএনএ ভাইরাস নিয়ে গবেষণা হয়েছিল। এই ভাইরাসগুলোকে রেট্রোভাইরাস (retrovirus) বলা হয়। এরা যে কোষে প্রবেশ করে, তার জিন-কে ছিনতাই করে নিজের কাজে লাগায়, সেই জিন-এর গঠন আর প্রকাশের নিয়ন্ত্রণকে ওলোটপালোট করে তাকে অংকজিন-এ পরিবর্তিত করে। কোষের কোথায় এই অংকজিন সৃষ্টি হয়, সেটা আমরা জেনে গেছিলাম। যেটা জানতাম না সেটা হলো অংকজিন-এ পরিবর্তিত হওয়ার আগে সেই জিনগুলোর ভূমিকা কি। আন্দাজ করতে পারছিলাম যে এই জিনগুলো কোষের নিয়ন্ত্রণক্ষমতার কেন্দ্রস্থল। তাই এদের কার্যক্রমে সামান্য রদবদলেও ক্যান্সার-এর মতো পরিণতি হতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এদের কাজটা ঠিক কি?
এর উত্তর পেতে গেলে বিবর্তন-এর আলোয় দেখতে হবে গোটা জীবজগতের নাট্যশালাকে। এই মুহূর্তে কতরকম প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়, সেখান থেকে শুরু না করে ভাবতে হবে এই অবিশ্বাস্য বৈচিত্র্য এলো কি করে। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব একটা বিরল ঘটনা, সেটা একবার কি বড়োজোর গুটিকয়েকবার হয়েছিল। প্রাণের একটা নিশ্চিত চিহ্ন হলো পরবর্তী প্রজন্মকে আনতে পারার ক্ষমতা অর্থাৎ বংশরক্ষা। পৃথিবীর প্রত্যেক আনাচে কানাচে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে সেইসব প্রজাতিই বংশ টিকিয়ে রাখতে পেরেছে যারা সেই পরিবেশের সবচেয়ে উপযুক্ত। প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হওয়ার পর কয়েকশো কোটি বছর ধরে বিভিন্ন পথে সেই প্রাণের ধারা ছড়িয়ে পড়েছে, তৈরী হয়েছে আজকের ব্যাকটেরিয়া, উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী।
বিবর্তন কখনো থেমে থাকে না। তাই অনেক প্রজাতির জীব, যারা একদিন ছিল, আজ আর নেই। একমাত্র জীবাশ্ম বা ফসিল-এর থেকে তাদের গঠন সম্পর্কে একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। কিন্তু সেসব না করে এখনকার বিবিধ প্রজাতির মধ্যে সাদৃশ্যগুলো দেখতে পারি। এই সাদৃশ্য দেখলে মনে হয় শুরুটা একই জায়গা থেকে হয়েছিল। এটা ভাবাই যায় যে একই পূর্বপুরুষের থেকে বিভিন্ন প্রজাতির ধারা শুরু হয়েছিল, বারে বারে পরস্পর-স্বাধীনভাবে প্রজাতিগুলোর সৃষ্টি হয়নি। সবার সূত্র যে একই, তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের জিনগত উপাদান, ডিএনএ। ডিএনএ অর্থাৎ ‘ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড’। যে কোনো জীবের কোষেই পাওয়া যায় নিজের প্রতিলিপি বানাতে সক্ষম এই বিশেষ অণুটিকে। ডিএনএ-র মধ্যে যে জিনগত তথ্য জমা থাকে, তাকে জমা করার অন্য কোনো রাসায়নিক উপায় অর্থাৎ অন্য কোনো ধরণের অণুও হতে পারতো। কিন্তু সেটা হয়নি। যে আদি-অকৃত্রিম কোষের থেকে সব জীবের সূত্রপাত হয়েছে, তাতে ঠিক ওইভাবে গঠিত ডিএনএ-ই ছিল, তাই আমাদের সবার মধ্যে ওই ডিএনএ-ই চলে আসছে। এর থেকে দুটো কথা বলা যায়। এক, একটা জিন-কে যদি অনেক ধরণের জীবের মধ্যে পাওয়া যায়, জিন-টা হয়তো সেই জীবগুলোর মধ্যে একই কাজ করে। দুই, জীবজগতে যত বেশি জীবের মধ্যে ওই জিন-টাকে পাওয়া যাবে, তত সম্ভাবনা বেশি যে সেই জিন-টা একটা খুব মৌলিক, সার্বজনীন কার্য সম্পন্ন করে।
তবে সত্তরের দশকের শেষের দিকে একটা প্রশ্ন রয়েই গেছিলো। ফলে বসা মাছি (fruit fly) কিংবা পাঁউরুটি বা মদ বানাতে ব্যবহৃত ঈস্ট (yeast), এইসব সরলতর জীবের মধ্যে যে জিন বা জৈব প্রক্রিয়া নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা যায়, তাই দিয়ে ক্যান্সার কিংবা মস্তিষ্কের ক্রমবৃদ্ধির মতো জটিল প্রক্রিয়া বোঝা সম্ভব কি? এইসব জটিল প্রক্রিয়াগুলো কি বিবর্তনের ধারায় পরের দিকে এসেছিলো, জটিল জীব আসার সাথে সাথে? নাকি প্রক্রিয়াগুলোর “আবিষ্কার” হয়েছিল একদম গোড়াতেই, এবং বিভিন্ন রকমের বহুকোষী জীবের মধ্যে এদের একই ভূমিকা রয়েছে, একটা অত্যন্ত সাধারণ এবং জরুরী ভূমিকা? আমরা বুঝতে পারছিলাম যে শেষের কথাটা ঠিক হলে আমরা কিছু সরল জীবের ওপর গবেষণা করে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবো। সেই গবেষণা থেকে পাওয়া জ্ঞানকে সম্বল করে মানুষের মতো জটিল জীবের কলকব্জাগুলোর রহস্যোদ্ঘাটন করতে পারবো।
সত্তরের দশকের শেষে এবং আশির দশকের শুরুতে, রেট্রোভাইরাস-এর দ্বারা ছিনতাইকৃত জিন-এর সাহায্যে বিজ্ঞানীরা মুরগিছানা, নেংটি ইঁদুর, ধেড়ে ইঁদুর, বেড়াল এবং বাঁদরের মতো মেরুদণ্ডী প্রাণীর জিনোম থেকে তাদের সেই জিনগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় আলাদা করার পদ্ধতি বার করলেন। কিন্তু তখনো অব্দি কেউ একটা ব্যাপার অনুসন্ধান করে দেখেননি: ক্যান্সারের জন্ম দেওয়া যায় যে জিনগুলোকে ছিনতাই করে, তাদের উপস্থিতি এবং সম্ভাব্য ভূমিকা শুধুমাত্র এই মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলোর মধ্যেই একচেটিয়া, নাকি আরো অনেক বহুকোষী জীবের মধ্যে এগুলো দেখা যায়।
ক্যান্সার-সৃষ্টিকারী জিন স্বাভাবিক অবস্থায় কি করে, সেই নিয়ে আমি ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলাম খুব সহজ একটা ধারণা দিয়ে। অংকজিন-এর মতো জিন যদি সরলতর জীবের জিনোম-এর মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে সেইসব জীবের ওপর গবেষণা করেই এদের কাজ বুঝতে পারবো। তারপর নাহয় দেখা যাবে এই গবেষণা থেকে তৈরী হওয়া ধারণা মানুষের ওপর কাজ করে কিনা। ধরো, একটা বাচ্চা তার প্রথম লেগো ব্লক খাপে খাপে জুড়লো। একবার যেই সে বুঝে গেলো ঠিক কিভাবে জোড়া যায়, তারপর যত কঠিন কলকব্জাই হোক না কেন, সে ট্রেন-এর চাকা হোক কি ঘড়ির ভিতরের কলকব্জা, সে দেখতে পাবে যে সবেতেই একই বুদ্ধি খাটে।
নিচুতলার জীবের মধ্যে অংকজিন-এর সন্ধান কিভাবে করবো? আজকে ব্যাকটেরিয়া, ক্রিমি থেকে শুরু করে মানুষের ডিএনএ-তে (DNA) একের পর এক যে অণুর শৃঙ্খল সাজানো আছে, তার সবটারই হদিশ আমরা জানি। এদেরকে বলে নিউক্লিওটাইড ক্রমবিন্যাস (nucleotide sequence)। কিন্তু সেই সময় যদিও টুকরো টুকরো ডিএনএ আলাদা করে উদ্ধার করা যেত, কোনটা যে কার পরে আর কার যে কি কাজ, তা জানা ছিল না। আমার প্রথম কাজ ছিল বিভিন্ন বহুকোষী জীবের থেকে ডিএনএ-র নমুনা সংগ্রহ করা। এই সংগ্রহ বানাতে আমি বস্টন আর কেমব্রিজ-এর কিছু গবেষণাগারে গেলাম যেখানে সামুদ্রিক আর্চিন (sea urchin), নেমাটোড ক্রিমি (nematode worms), মাছি (flies), এমনকি পাঁউরুটি বানাতে ব্যবহৃত ইস্ট-এর মতো এককোষী প্রাণী নিয়েও গবেষণা চলছে।
কি করে ক্যান্সার-সৃষ্টিকারী জিন-এর মতো একইরকম দেখতে জিন খুঁজতে বেরোলাম, সেটা বোঝাতে গেলে চট করে একবার মলিকুলার বায়োলজি-র চক্কর সেরে নিতে হবে। ডিএনএ-র একককে (unit) বলে নিউক্লিওটাইড। চার ধরণের নিউক্লিওটাইড হয়, তাদের সংক্ষেপে A, C, G আর T বলা হয়। যখন ডিএনএ-র ক্রমবিন্যাসের কথা বলি, তখন আসলে বলছি এই নিউক্লিওটাইডগুলোকে কোনটাকে কার পর জুড়ে একটা জীবের জেনেটিক তথ্যসম্ভার বানানো হলো। এবার একটা ক্যান্সার-সৃষ্টিকারী অংকজিনের কোনো জাতভাই ডিএনএ-তে আছে কিনা, সেটা নির্ণয় করতে হলে আগে লম্বা ডিএনএ-র ফিতেকে ছোট ছোট টুকরোয় ভাগ করতে হবে। আমরা একটা উৎসেচক (enzyme) ব্যবহার করলাম যেটা ডিএনএ-র ওপর ছটা বিশেষ নিউক্লিওটাইডকে একের পর এক দেখতে পেলেই সেখানটাতে ফিতেটা কেটে দেবে। যদিও ডিএনএ জোগাড় করতে হাজার হাজার কোষের নিউক্লিয়াস ব্যবহার করা হয়েছিল, এই পদ্ধতিতে সব কোষ থেকেই একই ধরণের টুকরো বেরিয়ে আসে। তুলনা করতে ধরো এমন একটা বিশ্বকোষ (encyclopedia) যেখানে বিশেষ ছটা অক্ষর একটা বিশেষ ক্রমে দেখা দিলেই অমনি একটা নতুন অনুচ্ছেদ (paragraph) চালু করা হবে। তাহলে ওই বিশ্বকোষের যতগুলো কপি-ই ব্যবহার করা হোক না কেন, সবকটা থেকে একই অনুচ্ছেদমালা বেরোবে।
এরপর টুকরোগুলোকে একটা agarose gel-এ রেখে একটা তড়িৎক্ষেত্রের সাহায্যে আধান বা চার্জ আর সাইজের ভিত্তিতে আলাদা করা হয়। gel-টাকে একটা বিশেষ ধরণের ব্লটিং পেপার-এ ফেললে আলাদা সাইজের টুকরোগুলো পেপার-এ আলাদা জায়গায় সেঁটে যায়। এইভাবে এই কাগজের ওপর জীবটার পুরো জেনেটিক উপাদান ধরা গেলো। এর পরের কাজ খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজতে নামা। এইটা দেখা যে নিচুতলার জীবের ডিএনএ-র মধ্যে এমন কোনো নিউক্লিওটাইড ক্রমবিন্যাস আছে কিনা, যেটার সাথে ইঁদুর কিংবা মুরগিছানা-র অংকজিন-এর মিল রয়েছে। ধরো তোমার কাছে একটা বইয়ের ইলেকট্রনিক সংস্করণ রয়েছে। অনেককাল আগে পড়া একটা বিশেষ কথা ওই বইটার মধ্যে খুঁজতে চাও। যেহেতু কথাটা তোমার একদম হুবহু মনে নেই, তুমি কম্পিউটারকে বলবে, তোমার যা মনে আছে তার সবচেয়ে কাছাকাছি কথাটা খুঁজে দিতে। আমরা খানিকটা এরকমই করলাম, এমন নিউক্লিওটাইডের ক্রমবিন্যাস খুঁজতে লাগলাম যার সাথে ক্যান্সার-সৃষ্টিকারী জিন-এর সম্পর্ক আছে। এই খোঁজের মূলে ছিল ডিএনএ-র ডাবল হেলিক্স আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা। ডিএনএ-র এককগুলোর কিছু বিশেষ রাসায়নিক ধর্ম রয়েছে – যার ফলে T জোড় বাঁধে A-এর সাথে আর C বাঁধে G-এর সাথে। এর ফলে তৈরী হয় ডিএনএ-র ডাবল হেলিক্স আকৃতি। ডাবল হেলিক্স-এর দুটো ফিতের একটার ওপর যে নিউক্লিওটাইডগুলো রয়েছে, তারা অন্য ফিতেটার নিউক্লিওটাইডগুলোর সাথে জোড় বেঁধে ফেলে (ছবিতে ডাবল হেলিক্স-এর আকৃতি দেখো)।

সেসময় অংকজিন-সমৃদ্ধ ডিএনএ-র টুকরো ব্যাপক হারে আলাদা করা এবং প্রস্তুত করা সম্ভব ছিল। মলিকুলার ক্লোনিং (molecular cloning) পদ্ধতি ব্যবহার করে সেইসব ডিএনএ টুকরোকে আলাদা করা হতো যেগুলোকে ছিনতাইকারী ভাইরাস-এর মধ্যে পাওয়া গেছে। মলিকুলার ক্লোনিং কি? এক অর্থে বলা যায় পদ্ধতিটা অনেকটা একটা হাজার পাতার বিশ্বকোষ থেকে একটাই পাতা খুঁজে বারবার ফটোকপি করার মতো। বিশ্বকোষের মধ্যে একটা পাতা আর একটা ইঁদুর কিংবা মানুষের সম্পূর্ণ জিনোম-এর মধ্যে একটা জিন, কাজটার জটিলতার তুলনা করলে এই দুটোর খুব একটা ফারাক নেই।
পদ্ধতিটার মূলে ছিল ডিএনএ-র প্রতিলিপিকরণ, যেখানে ডিএনএ-র ডাবল হেলিক্স-এর একটা ফিতেকে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে পরিপূরক ফিতেটার অনেকগুলো প্রতিলিপি বানানো যায়। এটা টেস্ট টিউব-এর মধ্যেই করা সম্ভব কিছু বিশেষ উৎসেচকের সাহায্যে। এবার সেই ডিএনএ-র চারটে একক-এর একটাকে যদি তেজস্ক্রিয় মৌল দিয়ে চিহ্নিত করা যায়, যত প্রতিলিপি তৈরী হবে, তারা সবাই তেজস্ক্রিয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবে। এইভাবে অংকজিন ধারক ডিএনএ-র অনেকগুলো তেজস্ক্রিয় প্রতিলিপি বানিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় আগের কাগজটার ওপর যেখানে একটা নিচুতলার জীবের ডিএনএ-র নানা সাইজের টুকরো সেঁটে আছে। আশাটা এইরকম যে এই তেজস্ক্রিয় প্রতিলিপিগুলো ডিএনএ টুকরো-র মধ্যে নিজেদের জাতভাইদের খুঁজে পেলে তাদের সাথে জোড় বাঁধবে। অংকজিন ধারক ডিএনএ আর কাগজে সেঁটে থাকা ডিএনএ যদি হুবহু এক নাও হয়, একাংশে মিল থাকলেই জোড় বাঁধার জন্য যথেষ্ট, এরকম আশা করা যায়।
যেই ভাবা, সেই কাজ। যে জিন-টা খুঁজছি, তাকে তেজস্ক্রিয় মৌল দিয়ে চিহ্নিত করে তাতে আগের কাগজটাকে চুবিয়ে দেওয়া হলো। এরপর কাগজের ওপর থেকে বাড়তি তেজস্ক্রিয় ডিএনএ ধুয়ে ফেললে, যদি কোনো তেজস্ক্রিয়তা তখনো ধরা পড়ে, তার মানে দাঁড়াবে যে অংকজিন ধারক ডিএনএ জোড় বাঁধার জন্য পরিপূরক ডিএনএ খুঁজে পেয়েছে। এরপর এই বন্ধনের প্রমাণ পেতে কাগজটাকে একটা সীল করা ক্যাসেট-এর মধ্যে একটা ফিল্ম-এর সান্নিধ্যে আনতে হবে। হাড় বা দাঁত এক্স-রে করার জন্য যে ফিল্ম ব্যবহার করা হয়, সেইরকম ফিল্ম। তেজস্ক্রিয় মৌল পড়ে থাকলে তা ফিল্মটার উপর উদ্দীপ্ত অবস্থার সৃষ্টি করবে। এই বিক্রিয়াটা অনেকটা আলোয় একটা ক্যামেরার ফিল্ম এক্সপোজ করার মতো। এরপর অন্ধকার ঘরে সেই ফিল্মটাকে ডেভেলপ আর ফিক্স করা হবে।
ডার্করুম-এর ক্ষীণ কমলা আলোয় যখন ফিল্ম ডেভেলপ আর ফিক্স করলাম, সেই আমার তেজস্ক্রিয় দাগ দেওয়া অংকজিন-এর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ। নিজের চোখে দেখলাম, ফিল্ম-এর ওপর একাধিক কাটা কাটা দাগ। একইরকম অনেকগুলো ডিএনএ টুকরোর উপস্থিতির জানান দিচ্ছে তারা! প্রত্যেকটা দাগ এমন একেকটা ডিএনএ টুকরোর পরিচয় দিচ্ছে যেটা অংকজিন-এর সাথে সফলভাবে জোড় বেঁধেছে। ডার্করুম-এর অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কাগজের কোন জায়গাটায় সেই ডিএনএ টুকরোগুলো আছে, তাই বলতে পারছিলাম না কোন জীবের ডিএনএ ক্রমবিন্যাস দেখছি। পরে ফিল্মটাকে লাইট বক্স-এর তলায় খুঁটিয়ে দেখলাম যখন, একদম পরিষ্কার হয়ে গেল যে ডিএনএ টুকরোগুলো এসেছে fruit fly বা ফলের মাছি, Drosophila melanogaster-এর থেকে।
এই আবিষ্কারের তাৎপর্য আমার কাছে তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট হয়ে গেলো। যে জিন উপরতলার জীবের মধ্যে ক্যান্সার সৃষ্টি করে, তা যদি ফলে বসা মাছির মধ্যেও পাওয়া যায়, তার মানে এই জিন-এর আবির্ভাব হয়েছে ষাট কোটি বছরেরও বেশি আগে। তখনও বিবর্তনের ধারায় মেরুদণ্ডী আর অমেরুদণ্ডীদের প্রভেদ শুরু হয়নি। এই প্রাগৈতিহাসিক উৎস থেকে আন্দাজ করা যায় যে জিনগুলো নিশ্চয় সব বহুকোষী প্রাণীর মধ্যেই একটা অত্যন্ত আবশ্যক কাজ সম্পন্ন করছে। আর যদি পরীক্ষানিরীক্ষার দিকটা দেখি, এই ফলের মাছিদের জিন-এর ওপর একশো বছরের বেশি কাটাছেঁড়া চলছে। অতএব এতদিনের উপলব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে মাছিদের জিনে অনেকরকম নকশাবাজি করা যাবে, যেগুলো থেকে শেষমেশ বোঝা যাবে মানুষের দেহে জিনগুলো আসলে কি কাজ করে।
যে কোনো বিজ্ঞানীর জীবনে কয়েকটামাত্র মুহূর্ত আসে যখন সে বুঝতে পারে যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আবিষ্কার করে ফেলেছে, এমন ঘটনা যার সাথে আগে কারো পরিচয় ঘটেনি। সেই আবিষ্কারের পুরো তাৎপর্য হয়তো তখনো স্পষ্ট নয়, কিন্তু সেটা প্রকাশমাত্রই সবার টনক নড়ে ওঠে। এইসব “আবিষ্কারের মুহূর্ত”-গুলোর জন্যেই আমরা বিজ্ঞানীরা অপেক্ষা করে থাকি। যদিও আবিষ্কারগুলোর ক্ষেত্র আলাদা, তবুও এই মুহূর্তগুলো আমার কাছে অনেকটা সেই ১৯২২-এর ২৬শে ডিসেম্বর-এ তুতানখামেন-এর সমাধি খুঁজে পাওয়ার মতন। সমাধিতে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, বাইরে বিশিষ্টজন আর পৃষ্ঠপোষকদের ভিড়, এমন অবস্থায় ব্রিটিশ পুরাতত্ত্ববিদ হাওয়ার্ড কার্টার রাজ শিলমোহর দেওয়া মাটির দেওয়ালে সামান্য একটা গর্ত তৈরী করলেন। একটা দমকা বাতাস বেরিয়ে এলো, তিন হাজার বছরের বদ্ধ বাতাস। এরপর তিনি সেই গর্ত দিয়ে একটা মোমবাতি প্রবেশ করালেন। আস্তে আস্তে যেই তার দৃষ্টি মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় অভ্যস্ত হয়ে উঠলো, কার্টার ঠাওর করতে পারলেন “আশ্চর্য সব জন্তু, মূর্তি, সোনা, সর্বত্র সোনার ঝিকিমিকি”। তার চোখেই প্রথম ধরা পড়লো সেই দৃশ্য, যে দৃশ্য মানবসভ্যতা নিয়ে আমাদের ধ্যানধারণার একটা মূল স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াবে।
১৯৮১-র গ্রীষ্মকালে, মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্যান্সার-সৃষ্টিকারী জিন ফলের মাছির মধ্যে আবিষ্কার করার পর, আমি ইজরায়েল -এর ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউট-এ আমার ল্যাব স্থাপন করলাম। পরবর্তী তিরিশ বছর আমি মাছির জীবনচক্রে এই জিনগুলোর ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করে গেছি। আমার গবেষণাপদ্ধতিটাকে এক অর্থে “উল্টোপথে জেনেটিক্স” (reverse genetics) আখ্যা দেওয়া যায়। এতে শুরু হয় একটা জানাশোনা জিন থেকে, তারপর তাতে কিছু পরিবর্তন (mutation) করে সেই পরিবর্তনের পরিণাম কি হলো, সেইটা দেখা হয়। এই পদ্ধতিতে জীবের মধ্যে জিন-টার ভূমিকা কি, সেটা আগেভাগে জানা থাকেনা। জিন-টাকে এক অর্থে “ভরসা করে”, হাতে যা প্রযুক্তি রয়েছে, তার সাহায্যে বিশ্লেষণ করে যেতে হয়, এই আশায় যে, কোন জৈবিক প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকা রয়েছে, সেটা একদিন ঠিক উদ্ধার হবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে আমি যাত্রা শুরু করলাম মেরুদণ্ডীদের মধ্যে ক্যান্সার-সৃষ্টিকারী জিন দিয়ে কিন্তু গিয়ে পড়লাম সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা জগতে। ফলের মাছির ভ্রূণ অবস্থায় তার কোষগুলো ঠিক কিভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলে, সেটাই হয়ে গেল আমার পরবর্তী জীবনের গবেষণা।
এই গবেষণাপদ্ধতির একটা পরিপূরক পদ্ধতি রয়েছে, সেটা হলো “সোজাপথে জেনেটিক্স” (forward genetics)। এতে প্রথমে কোন জৈবিক প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা হবে, সেইটা আগে ঠিক করে নেওয়া হয়। এরপর সেইসব জিনগত পরিবর্তনের খোঁজ করা হয় যেটা সেই প্রক্রিয়াতে বাধ সাধবে। অর্থাৎ এখানে প্রক্রিয়াটা জানা আছে, কিন্তু তার পেছনে কার্যরত জিনগুলোকে জানা নেই। সত্তরের দশকের শেষে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ানা নিউসলেন-ভোলহার্ড আর এরিক উইসআস ফলের মাছির ভ্রূণ অবস্থার আড়ালে কোন কোন জিন দায়ী সেটা এই সোজাপথে জেনেটিক্স করেই বার করেছিলেন। সেই ভ্রূণর কারুকার্যের (embryonic pattern) পেছনে বেশিরভাগ জিনকেই ওনারা চিহ্নিত করতে পারলেন। এরপর সেই জিনগুলোকে আলাদা করতে এবং তাদের আণবিক গঠন নির্ণয় করতে হৈহৈ পড়ে গেল। জিনগুলোর আণবিক গঠন যত স্পষ্ট হলো, দেখা গেল যে এই জিনগুলো আর আমার ‘উল্টোপথে জেনেটিক্স’ পদ্ধতিতে বার করা জিনগুলো একই। আমার পথটা উল্টো কারণ সেই জিনগুলোর হদিশ আমি মেরুদণ্ডীদের ক্যান্সার-সৃষ্টিকারী জিন থেকে শুরু করে পেয়েছিলাম। যাইহোক, আশির দশকের শেষের দিকে গিয়ে আলাদা জায়গা থেকে শুরু করা এই দুটো বিপরীতগামী পদ্ধতির সঙ্গম ঘটলো।
সেই থেকে অনেকগুলো ল্যাব-এর গবেষণা এটাই সাব্যস্ত করেছে যে এই দুই পদ্ধতিতে বার করা জিন আসলে কোষের যোগাযোগব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের জন্ম দেয়। এই যোগাযোগের মাধ্যমেই ভ্রূণ অবস্থায় বিভিন্ন কোষ নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করে একটা ভ্রূণ-র জটিল কারুকার্যের সৃষ্টি করে। এই জিনগুলো আছে সব বহুকোষী জীবের মধ্যেই, অতএব বলা যায় এই কোষীয় যোগাযোগের প্রক্রিয়াগুলোও হয়তো সর্বজনীন। সত্যি বলতে কি, বহুকোষী হওয়ার পিছনেও রয়েছে এই জিনগুলোই। একটা ভ্রূণের বিকাশের যে জটিল প্রক্রিয়া রয়েছে, সেটা সুনিশ্চিত এবং সুশৃঙ্খল কারণ কোষগুলোর আচরণ নির্ণয় করে দেয় কিছু স্পষ্ট “নিয়মকানুন”, যেগুলো সেই জীবের ডিএনএ-র মধ্যে গাঁথা আছে। এই নিয়মগুলো মেনে চললেই আস্তে আস্তে একটা ভ্রূণের কারুকার্যগুলো ফুটে ওঠে।
আণবিক স্তরে কোষেরা কিভাবে যোগাযোগ করে, সেই পদ্ধতিগুলো চিহ্নিত করা এবং সাথে সাথে এটাও বোঝা যে সেগুলো সব বহুকোষী জীবের মধ্যেই বর্তমান, এখানেই বোধহয় প্রাণের নকশার অনুসন্ধানকার্য একটা নতুন বাঁক নিলো। এর ফলে জীববিজ্ঞানও একটা সর্বজনীন শাখায় পরিণত হলো কারণ দেখা গেলো যে ভিন্ন ভিন্ন জীবের আপাতভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার আড়ালে একই জিন এবং একই কোষীয় যোগাযোগব্যবস্থা রয়েছে।
(‘Life’s blueprint’ বইটা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছে ‘বিজ্ঞান’ টীম-এর অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং কুণাল চক্রবর্তী।)

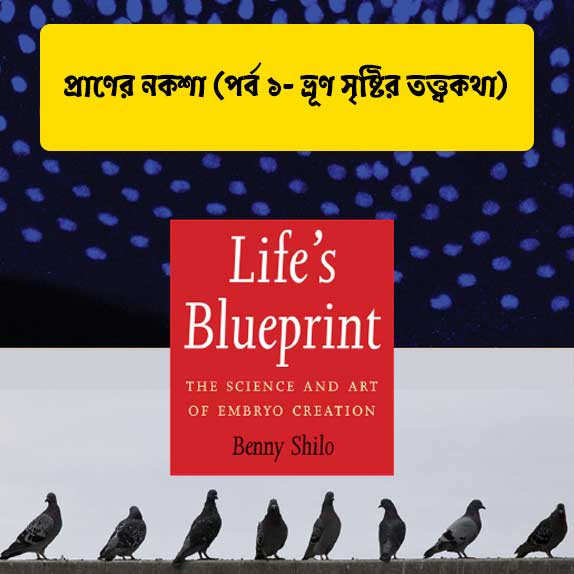
Great buddy keep doing the good works Education News Of India