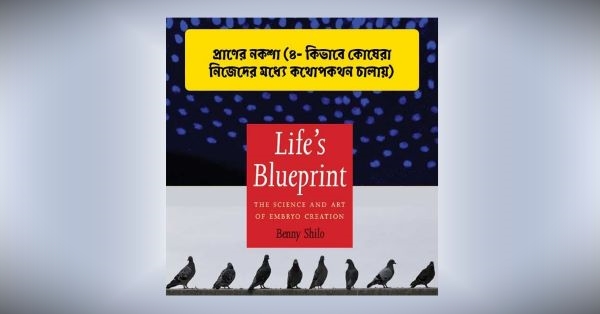(নিচের পোস্ট-টা মলিকুলার জেনেটিক্স গবেষক বেনি শিলো-র লেখা ‘Life’s Blueprint’ বইটার চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ। বইটা সম্বন্ধে আরো জানতে ভূমিকাটি দেখুন।)
আগের অধ্যায়ে আমরা স্পিমান আর মানগোল্ড-এর ১৯২৪-এর পরীক্ষাটার তাৎপর্যের কথা বলেছিলাম। এই অব্দি বুঝেছিলাম যে কোষের ভাগ্য আগাগোড়া পূর্বনির্ধারিত নয়। “বড় হয়ে কি হবে”, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোষেরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে এবং প্রভাবিত হয়। অন্যভাবে বললে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ভুলে একটা কোষ একটা পূর্বলিখিত ভাগ্যের দিকে ধেয়ে চলে না। বরং সেই পরিবেশের কাছ থেকে পাওয়া নির্দেশের ওপরই সে ভরসা করে থাকে। এই ব্যাপারটা বুঝতে আমরা আমাদের পুরোনো সমাজের সাথে আধুনিক সমাজের তুলনা করতে পারি। এককালে সমাজে শ্রেণীবিভাগ ছিল। কে কোন পথে যাবে, তার পেশা কি হবে, সব জন্ম থেকে ঠিক করে দেওয়া হতো। আজকের সমাজে আমাদের যোগ্যতা এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে আদানপ্রদানই বেশিরভাগ সময় ঠিক করে দেয় একজন ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছতে পারবে।
এই ধারণাটা ভ্রূণবৃদ্ধির রহস্যোদ্ধারে আমাদের যে কতটা এগিয়ে দিয়েছিল, সেটা বলে বোঝানো মুশকিল। ভ্রূণবৃদ্ধি বুঝতে এখন প্রয়োজন হয়ে উঠলো সেইসব নির্দেশগুলোর হদিশ পাওয়া, যেগুলো কোষেরা অনবরত একে অপরকে পাঠিয়ে চলেছে। কোষেদের এই ভাষা বুঝতে পারা জরুরি হয়ে পড়লো কারণ ডিএনএ-র তথ্য শুধুমাত্র কোষেদের এই আদানপ্রদানগুলোকে কিছু নিয়মকানুনে বেঁধে দিয়ে ভ্রূণর শেষের অবস্থাটাকে নির্ণয় করে। এর বাইরের আর কোনো খুঁটিনাটিতে সে হস্তক্ষেপ করে না।
যদি প্রত্যেকটা কোষের একেবারে পূর্বলিখিত নিয়তি থাকতো, তাহলে একটা কোষ হারালেই শেষের নকশাটা ভয়ানকভাবে ঘেঁটে যেত। অপরদিকে, যদি কোষেদের অনেকগুলো পথে যাওয়ার সুযোগ থাকে, একটা কোষ হারালে অন্যেরা তার জায়গা নিতে পারে।
এই যে কোষেদের ছেড়ে দেওয়া হয় নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নিতে, এতে কিন্তু লাভই হয়। ক্রমবৃদ্ধির জটিল পদ্ধতিটা খুচরো ভুলচুকের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকে। যদি প্রত্যেকটা কোষের একেবারে পূর্বলিখিত নিয়তি থাকতো, তাহলে একটা কোষ হারালেই শেষের নকশাটা ভয়ানকভাবে ঘেঁটে যেত। অপরদিকে, যদি কোষেদের অনেকগুলো পথে যাওয়ার সুযোগ থাকে, একটা কোষ হারালে অন্যেরা তার জায়গা নিতে পারে। সেই যে বলে, এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে চলে গেলে অন্য কেউ তার জায়গায় আসতে পারবে না, এটা খানিকটা সেইরকম।
স্পিমান আর মানগোল্ড-এর পরীক্ষাগুলো যতই নাটকীয় হয়ে থাকুক না কেন (গোসাপ-এর ধড়ে দুটো মাথা গজানোর থেকে নাটকীয় কিছু হতে পারে কি?), তার থেকে পাওয়া সিদ্ধান্তগুলো ঝুলে রইলো পাঁচ দশক ধরে। এই বিরতির কারণ হলো, কোষেদের যোগাযোগব্যবস্থা ও একে অপরকে নির্দেশ দেওয়ার ব্যাপারটা জানা থাকলেও, কারা সেই আদানপ্রদান চালায়, সেটা জানা ছিল না। অর্থাৎ, আণবিক স্তরে এই যোগাযোগব্যবস্থার উপাদানগুলোকে জৈবরাসায়নিকভাবে আলাদা করা যাচ্ছিলো না। আসলে, এই উপাদানগুলো যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তারা কিন্তু থাকতে পারে খুব স্বল্প পরিমাণে। যেভাবে তাদের সনাক্ত করা যায়, সেই পদ্ধতিগুলো (biological assay) মোটেই সহজ নয়। অন্যভাবে বললে, তারা কিরকম হতে পারে, সে ব্যাপারে আর কোনো ধারণা না থাকলে, কোষের গুচ্ছের উপাদানের মিশ্রণে কোষীয় যোগাযোগব্যবস্থার কান্ডারীদের খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এটাকে তুলনায় করা যায় একটা সেলফোনকে গুঁড়ো গুঁড়ো করার সাথে। আগে থেকে কিছু না জানা থাকলে শেষের ঘ্যাঁট-টার মধ্যে কোনটা ফোনের মাস্টার চিপ ছিল, সেটা বলতে পারবে কি?
বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত জিনগত পদ্ধতিতে বার করলেন কোন পথে (pathway) কোষেরা নিজেদের মধ্যে কথোপকথন চালায়। একটা জীবের জিনগত গঠনকে বলে জেনোটাইপ (genotype) আর সেটা নির্ণয় করে জীবের শেষের চেহারাটা কেমন হবে, যাকে বলে ফেনোটাইপ (phenotype)।
বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত জিনগত পদ্ধতিতে বার করলেন কোন পথে (pathway) কোষেরা নিজেদের মধ্যে কথোপকথন চালায়। একটা জীবের জিনগত গঠনকে বলে জেনোটাইপ (genotype) আর সেটা নির্ণয় করে জীবের শেষের চেহারাটা কেমন হবে, যাকে বলে ফেনোটাইপ (phenotype)। জিনগত বিশ্লেষণ করতে গেলে জিন-এ পরিবর্তন (mutation) আনতে পারা চাই এবং তারপর সেই পরিবর্তন কিভাবে প্রকাশ পায়, সেইটে ঠাওর করতে পারা চাই। যেহেতু জিন-এর ক্রমবিন্যাস নির্ণয় করে শেষের প্রোটিন কিরকম হবে, এই ক্রমবিন্যাসে সামান্য রদবদল হলে সেটা প্রোটিন-এ ধরা পড়বে। পরিবর্তনটা কোথায় হচ্ছে, তার উপর ভিত্তি করে শেষের প্রোটিনে উনিশ বিশ তফাৎ হতে পারে (একটা গোটা বাক্যে একটা অক্ষর পাল্টালে যেরকম হয়), আবার গোটা প্রোটিন-টার কাজে গোলযোগ বাধতে পারে। যদি একটা মোক্ষম প্রোটিন-এ হাত পড়ে, জীবের চেহারায় কি কার্যক্ষমতায় একটা পরিবর্তন আসার প্রবল সম্ভাবনা থাকে (অন্যভাবে বললে, একটা নতুন ফেনোটাইপ-এর সৃষ্টি হয়)। এর দারুণ উদাহরণ হলো ১৯১০ সালে টমাস এইচ. মরগ্যান-এর প্রথম জিনগত পরিবর্তনের (mutation) আবিষ্কার যেখানে ফলের মাছি, Drosophila-তে, একটিমাত্র জিন পাল্টাতে চোখের রং লাল থেকে সাদা হয়ে গেছিলো। এই জিনগত পরিবর্তনটা, যাকে শেষের ফেনোটাইপ-এর নামে “সাদা” (white) বলে ডাকা হয়, এটাকে আলাদা করাই জৈবিক প্রক্রিয়ার জিনগত ভিত্তি সন্ধানের একটা উদাহরণ। বিপুল সংখ্যক মাছির কিছুর মধ্যে এই পরিবর্তনটার আবির্ভাব হঠাৎ করেই হয়েছিল। কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্মের মধ্যে এই পরিবর্তিত জিন-এর উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছিল, স্রেফ ওই সাদা চোখের রং-এর কারণে। আজ পর্যন্ত শয়ে শয়ে গবেষকদল এই বিশেষ পরিবর্তনটাকে তাদের গবেষণায় ব্যবহার করেছেন। তাহলে দাঁড়ালো এইরকম: যে জিন-টার পরিবর্তনের ফলে ওই ফেনোটাইপটা দেখা গেল, সেটার নিশ্চই গুরুতর ভূমিকা আছে চোখের রং তৈরীর পিছনে। কারণ ওই জিনটা না থাকলে চোখে কোনো রং দেখা যায় না। পরে ওই “সাদা” জিন-টার উপর আরো কাটাছেঁড়া করে দেখা গেছিলো যে আণবিক স্তরে সত্যিই সেখানে রং সৃষ্টি এবং বহনের ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যভাবে বললে, একটা জিন-এর অনুপস্থিতিতে যে ফেনোটাইপ-এর জন্ম হয়, সেটাই জিন-টাকে একটা প্রক্রিয়ার আড়ালে নাটের গুরু হিসেবে চিনিয়ে দেয় (নিচের ছবিটা দেখো)।

একটা জিন-কে সরিয়ে দিলে দেহে যে খুঁত তৈরী হয়, তার থেকেই বোঝা যায় জিন-টার কি ভূমিকা ছিল। যেরকম ভিজে সিমেন্ট-এর ওপর একটা পাতা এসে পড়লে, সেটা পরে সরিয়ে নিলে তার অনুপস্থিতিটা পাকাপাকিভাবে ধরাশায়ী হয়ে থাকে (B. Shilo, Hampi, India)।
এটা অনেকটা সেই ছোটবেলার খেলাটার মতো যেখানে কোনো একজন একটা বিশেষ অঙ্গভঙ্গি করে আর ঘরের মধ্যে বাকিরা তাকে অনুকরণ করে। সেই ঘরে ঢুকলে তোমার বোঝার উপায় নেই কাকে অনুকরণ করা হচ্ছে। তুমি হয়তো আন্দাজে একজনকে ঘর থেকে বার করে দিলে। বাকিরা যদি তাদের কীর্তি চালিয়ে যায়, তাহলে বোঝা যাবে যে নাটের গুরু এখনো ঘরেই আছে। তুমি তখন আরেকজনকে বার করলে। এইভাবে করতে করতে যখন আসল লোকটাকে ঘরছাড়া করবে, ডামাডোল থামবে এবং অমনি তুমি বুঝে যাবে তার ভূমিকা কি ছিল।
শুরু থেকেই পরিবর্তনগুলো জিন ধরে করা হয়না। প্রথমে ঠিক করা হয়, অমুক ফেনোটাইপ-এর ওপর মনঃসংযোগ করা হবে। এরপর জিন সরিয়ে নেওয়া হয় বা তাতে খুঁত সৃষ্টি করা হয় যতক্ষণ না সেই ফেনোটাইপ-টা দেখা যাচ্ছে। যেই সেটা দেখা যায়, স্পষ্ট হয়ে যায় একটা প্রক্রিয়ার পেছনে জিনগত সার্কিট-টা কিরকম ছিল।
কিন্তু আগে থেকে যদি নাই জানি যে কোন জিন আর প্রোটিনগুলো একটা জৈবিক প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী, তাহলে সেই জিন-এ পরিবর্তন আনবো কি করে? এর উত্তর হলো, শুরু থেকেই পরিবর্তনগুলো জিন ধরে করা হয়না। প্রথমে ঠিক করা হয়, অমুক ফেনোটাইপ-এর ওপর মনঃসংযোগ করা হবে। এরপর জিন সরিয়ে নেওয়া হয় বা তাতে খুঁত সৃষ্টি করা হয় যতক্ষণ না সেই ফেনোটাইপ-টা দেখা যাচ্ছে। যেই সেটা দেখা যায়, স্পষ্ট হয়ে যায় একটা প্রক্রিয়ার পেছনে জিনগত সার্কিট-টা কিরকম ছিল। তাই, ফলের মাছির চোখের রং না তার ডানার গড়ন, আগে ফেনোটাইপ-টা ঠিক করলে আপনাআপনি ঠিক হয়ে যায় কোন জিনগুলো নিয়ে আরো গভীরে গবেষণা করা হবে। একেকটা করে জিন-কে নিষ্ক্রিয় করে জীবের কোনো নির্দিষ্ট কলা (tissue) বা দশায় (stage) লক্ষ্য রাখা হয়। দেখা হয় সেখানে কোনো ফেনোটাইপ-এর পরিবর্তন হচ্ছে কিনা। এলোমেলো ভাবে জিনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে, ফেনোটাইপ দেখে দেখে জিন ছেঁকে নেওয়াকে বলে জেনেটিক স্ক্রিন, বাংলা করা যেতে পারে “জিনগত ছাঁকনি” (genetic screen)।
কিভাবে এই জেনেটিক স্ক্রিন করা হয়? একটা জীবের জিনোম বা জিনগত উপাদানে আয়নিকরণক্ষম (ioninizing) তেজস্ক্রিয় রশ্মি কিংবা রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে কিছু এলোপাথাড়ি পরিবর্তনের সৃষ্টি করা হয়। ডিএনএ প্রতিলিপিকরণে যেভাবে হুবহু প্রতিলিপি তৈরী হওয়ার কথা, সেইটা আর হয়না, একটু রকমফের দেখা যায়। জিনোম-এর এই “কলঙ্ক” চালান হয় শুক্রাণু আর ডিম্বাণুতে থাকা ডিএনএ-র মধ্যেও। যেহেতু এই শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর থেকে সন্তানের জন্ম শুরু, পরিবর্তিত জীবগুলোর সন্তানদের মধ্যে প্রত্যেকটা কোষের ডিএনএ-তেই ওই পরিবর্তনটাকে দেখা যায়। এইভাবে একটা পরিবর্তনকে পাকাপাকিভাবে ধরে রাখা যায় কারণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম পরিবর্তনটা এবার নিশ্চিতভাবে চালান হতে থাকবে।
মনে করে দেখো, বহুকোষী জীবের জিনোম-এ কিন্তু একেকটা ক্রোমোসোম-এর দুটো কপি আছে, একটা আসে শুক্রাণুর থেকে আর অন্যটা আসে ডিম্বাণুর থেকে। অতএব, যদি একটা অতীব প্রয়োজনীয় জিন-এর পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে বিকল করেও দেওয়া হয়, জোড়ার অন্য জিন-টা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সজাগ থাকে এবং সেই জিনগত কাজের “শূন্যস্থান” পরিপূরণ করে। অন্যভাবে বললে, একটা কোষ কিংবা জীব নিজের জিন-এ ক্ষতিকারক পরিবর্তন নিয়েও বহালতবিয়তে থাকতে পারে।
যথেষ্ট সংখ্যক পরস্পর-স্বাধীন পরিবর্তন সৃষ্টি করে তার ফলাফল খতিয়ে দেখার পর বলা যেতে পারে যে একটা জেনেটিক স্ক্রিন-এ একটা প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী বেশিরভাগ জিন-কেই চিহ্নিত করা গেছে। স্ক্রিন-টাকে তখন সম্পূর্ণ বা স্যাচুরেটেড (saturated) বলা হয়। আগের উদাহরণটাই ধরা যাক যেখানে ঘরের মধ্যে কে ডামাডোল শুরু করেছিল, তাকে চিহ্নিত করতে হবে। যদি ঘরে বিশজন থাকে আর তুমি এক দুজনকে বার করে দাও, তোমার নাটের গুরুকে ধরতে পারার সম্ভাবনা কম। কিন্তু যদি বিশজনকেই বার করে দাও এক এক করে, তাহলে তাকে একটা না একটা সময় ধরতে পারবেই। তখন তোমার স্ক্রিন-টা সম্পূর্ণ কারণ যতগুলো সম্ভাবনা ছিল, সব তোমার পরীক্ষা করে দেখা হয়ে গেছে।
এই ধরণের জেনেটিক স্ক্রিন-এ কি বেরোবে সেব্যাপারে গবেষকের কিন্তু আগে থেকে কোনো ধারণাই থাকে না। বিশেষ করে যখন কোনো একটা জটিল প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা হচ্ছে, তখন একদম খোলা মনে কাজ শুরু করতে হয়। এই প্রক্রিয়াগুলো এতটাই জটিল যে বাস্তবে কি ঘটছে, সেই ধারণা আগে থেকে তৈরী করা প্রায় অসম্ভব। তাই যারা এই কাজটা করছেন, তাদের মধ্যে কোনো বিশেষ প্রক্রিয়ার প্রতি পক্ষপাত থাকলে চলবে না। স্ক্রিন-এ যেসব পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা যায়, সেগুলোই খোলসা করে দেয় একটা প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।
সত্তরের দশকের শেষের দিকে, ক্রিস্টিয়ানা নিউসলেন-ভোলহার্ড আর এরিক উইসআস এরকমই একটা জেনেটিক স্ক্রিন করেছিলেন ফলের মাছির উপর। আঠারো হাজার জাতের(strain) মাছির সৃষ্টি করলেন তারা, প্রত্যেকটার জিনোম-এ এক বা একাধিক পরিবর্তন রয়েছে। আজ আমরা জানি যে এই প্রজাতির মাছিতে তেরো হাজার মতো জিন রয়েছে। তাই ওনারা যে সংগ্রহটা বানিয়েছিলেন, তাতে খুব সম্ভবত বেশিরভাগ জিন-এই হাত দেওয়া গেছিলো। এই নিয়ে ওরা জেনেটিক স্ক্রিন করলেন। ওনাদের লক্ষ্য ছিল আকাশছোঁয়া, একেবারে ভ্রূণর নকশা তৈরীর পিছনে থাকা জিন-গুলোকে চিহ্নিত করা। হ্যাঁ, ফলের মাছি একটা সরলতর মডেল অর্গানিজম (model organism), তাদের ভ্রূণের বিকাশ সম্পূর্ণ হতে লাগে মাত্র চব্বিশ ঘন্টা। কিন্তু সম্পূর্ণ হওয়ার পর সেই ভ্রূণর মধ্যে পঞ্চাশ হাজার কোষ থাকে, বিশেষীকৃত কলার সবটাই তাতে ধরা পড়ে, তাই প্রক্রিয়াটা মোটেই হ্যালাফেলা করার মতো নয়। এই যুগান্তকারী কাজের জন্য ১৯৯৫ সালে তাঁদের নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়।
বিজ্ঞানীদের জিন-এর সংগ্রহে প্রত্যেকটা স্ট্রেন-এ একটা জিন ছিল স্বাভাবিক আর তার জুড়িদার-টা পরিবর্তিত (যে কোনো একটা জিন-এ পরিবর্তন-টা হতে পারে)। কিন্তু যখন একই ধারার স্ত্রী-পুরুষের মিলনে সন্তান তৈরী হয়, কিছু সন্তানের দু-কপি জিন-ই ডিফেক্টিভ বা পরিবর্তিত হতে পারে। জিন-টা যদি একটা জরুরি জিন হয়, তাহলে এরকম ক্ষেত্রে পরবর্তী জীবিত প্রজন্ম তৈরীই হবে না। একটা জিন জরুরি হতে পারে কারণ সে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াতে মধ্যস্থতা করে, যেমন বিপাক বা মেটাবলিজম (metabolism) কিংবা কোষের ভিতর গঠনমূলক কার্যে। কিন্তু গবেষকদের জেনেটিক স্ক্রিন-এর মূল লক্ষ্যবস্তু সেইসব জিন ছিল না। তারা খুঁজছিলেন সেইসব জিন যা ভ্রূণর নকশাকে প্রভাবিত করে।
কিরকম নকশা? ফলের মাছির স্বাভাবিক ভ্রূণবিকাশের সময়, ভ্রূণর বাইরের খোসার কোষগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে ভ্রূণর ভিতর আলাদা আলাদা ভাগ বা খুপরি তৈরী হয়ে যায়। একেকটা ভাগ কোথায় অবস্থিত, মাথার না ল্যাজের দিকে, পেটের না পিঠের দিকে, সেই অনুযায়ী তারা একেকটা আকৃতি ধারণ করে। খোসার কোষগুলো থেকে নিঃসৃত হয় একটা শক্ত সুরক্ষাপ্রদানকারী স্তর, যাকে কিউটিকল (cuticle) বলা হয়। এটাকে ভ্রূণের বাইরের দিকের কাঠামো হিসেবে ভাবতে পারো। এই স্তরটার প্রধান রসদ হলো একটা জড় পদার্থ, কাইটিন (chitin), এর ফলে স্তরটা মজবুত আর টেকসই হয়। এই স্তরটার গঠন কিরকম হবে, সেটা নির্ভর করে ভিতরের খোসার কোষগুলোর উপর। এই কিউটিকল নামক “খোলস”-ই শেষপর্যন্ত ভ্রূণ বিকাশের ধাঁধাটার একটা সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করলো (নিচের ছবি দেখ)। ভ্রূণ মরে যাওয়া কিংবা মিলিয়ে যাওয়ার পরও তাদের বাইরের খোলস-টা কিন্তু দিব্যি মজবুত আর টেকসই থাকে। তাই গবেষকরা সেই খোলসটাকে নিয়ে দেখতে পারেন জিন পরিবর্তনের ফলে কোথায় গোলমাল দেখা দিলো, ল্যাজের অভাবে হলো নাকি একজোড়া মাথা গজালো।

ফলের মাছির ভ্রূণর বাইরের স্তরে একটা শক্ত আবরণ বা “খোলস” নিঃসৃত হয়। খোলসটা কিরকম হবে, সেটা ভিতরের কোষগুলোর কি দশা, তার উপর নির্ভর করে। আঠারো হাজার মাছির স্ট্রেন-এ আনাড়িভাবে জিন-এ পরিবর্তন ঢুকিয়ে ভ্রূণের নকশায় খুঁত সন্ধানের চেষ্টা করা হলো। এইভাবে জেনেটিক স্ক্রিন করে গবেষকরা কিছু জিনগত পরিবর্তন (mutation) খুঁজে পেলেন যেগুলো এই ধরণের খুঁতের জন্ম দেয়। এর থেকে তারা যেসব জিনগুলোকে চিহ্নিত করলেন, তারা কোষীয় যোগাযোগব্যবস্থার মধ্যমণি কিছু প্রোটিনের জন্ম দেয়। যদিও বাইরের খোলসটা আসল ভ্রূণর একটা “ছায়া” মাত্র, তবু তার থেকেই ভ্রূণ সৃষ্টির বেশিরভাগ উপাদানের সুলুকসন্ধান পাওয়া গেল।
উপরের ছবি: ফলের মাছির ভ্রূণর বাইরের “খোলস” (B. Schweitzer and B. Shilo, Weizmann Institute)। নিচের ছবি: ছায়ার থেকেও কিন্তু গভীরে থাকা আসল সম্পর্কটা বোঝা যায় (B. Shilo, Israel Museum, Jerusalem)।
শুরুতে জানা ছিল না মাছির জিনোম-এ তেরো হাজার জিন-এর মধ্যে কতগুলো ভ্রূণের সূক্ষ্ম নকশা তৈরীর কাজে নিয়োজিত। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে মাত্র দুশোর কাছাকাছি জিন ছিল যাদের পরিবর্তন করতে নকশায় খুঁত দেখা গেল। যেহেতু বেশিরভাগ জিন-এই হাত পড়েছিল এই স্ক্রিন-এ, স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে ভ্রূণর জটিল গঠন এবং আকৃতির পিছনে ওই অল্পসংখ্যক জিন-ই রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার আলাদা আলাদা জিন-এর পরিবর্তন সত্ত্বেও একইরকম খুঁত দেখা গেল। এর মানে, জিনগুলো একই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। অন্যভাবে বললে, জিনগুলো একের পর এক ক্রমানুসারে কাজ করে একটাই প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করতে।
কমলালেবু চাষের কথা ভাবো। কল্পনা করে দেখো ঠিক কি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাষের ক্ষেত থেকে শুরু করে একদম শেষে একটা কমলালেবুকে বাজারের তাকে পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার কোথাও একটা যদি ব্যাগড়বাই হয়, জলের অভাব কিংবা অনুপযুক্ত বাতাবরণ থেকে শুরু করে লেবু-চালানকারী ট্রাকে যান্ত্রিক গোলযোগ, সবেতেই ফল কিন্তু একই হবে: বাজারের তাক লেবুশূন্য! অর্থাৎ প্রত্যেকটা ধাপই গোটা প্রক্রিয়াটার জন্য মহামূল্যবান। যেসব জিন-এর অনুপস্থিতিতে একই ধরণের খুঁত তৈরী হয়, তাদের সকলকে একই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপের প্রতিনিধি বলা যায়। এবার, এই জিনগুলোকে আলাদা করার পর সহজেই বার করা যায় এরা কিরকম প্রোটিন বানায়। সেইসব প্রোটিনের গঠন দেখলে একটা আন্দাজ পাওয়া যায় কোষের কোথায় এদের অবস্থান এবং আণবিক স্তরে কিভাবে এরা কাজ করতে পারে। দেখা গেলো যে এইসব প্রোটিনের মাধ্যমেই কোষেরা নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করে। স্পিমান যে সম্ভাব্য যোগাযোগপদ্ধতির কথা একদিন বলেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল, নাড়িভুড়ি বার করে দেখাও গেল। কোষের কথপোকথনের “ভাষা” চলে এলো নাগালের মধ্যে।
কোষেদের এই যোগাযোগব্যবস্থাকে আণবিক স্তরে কিভাবে দেখবো? সব কোষের বাইরেই একটা মেমব্রেন (membrane) বা কোষপর্দা রয়েছে। এই মেমব্রেন বহু ফ্যাট-যুক্ত অ্যাসিড (fatty acid) দিয়ে গড়া, একেকটা অ্যাসিড যেখানে ইয়ালম্বা একটা কার্বন পরমাণুর শৃঙ্খল। বাইরের এই fatty acid আর কোষের ভিতরের জলীয় পরিবেশ, এই দুই পরিবেশের মধ্যে একটা স্পষ্ট বিভেদ রয়েছে। ফলে মেমব্রেন-টাকে কোষ আর তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে একটা গণ্ডি বলা যেতে পারে। এই মেমব্রেন-এর সৌজন্যেই কোষ নিজের ভিতরের স্বতন্ত্র পরিবেশকে অক্ষুন্ন রাখতে পারে। কিছু জিনিসকে সে বেছেবুছে ভিতরে কব্জা করে রাখতে পারে আর বাকি অনভিপ্রেত জিনিসকে বহিষ্কার করে দিতে পারে।
এই মেমব্রেন-এ আছে বিশেষ কিছু প্রোটিন যারা বিবিধ রকমের কাজ করে। আমাদের আলোচনার জন্য যে শ্রেণীর প্রোটিন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাদেরকে বলে রিসেপ্টর (receptor) বা গ্রাহক। এরাই কোষীয় মেমব্রেন-এর বাইরে থেকে ভিতরে সংকেত পাচার করে। এই রিসেপ্টর-গুলো মেমব্রেন-এ গেঁথে আছে তবে এদের কিছুটা বাইরে বেরিয়ে থাকে। এই বেরিয়ে থাকা অংশটার সাথে অন্যান্য কোষ থেকে নিঃসৃত হরমোন জাতীয় কিছু প্রোটিন-এর মুলাকাত ঘটে। একবার রিসেপ্টর আর প্রোটিন-এর যোগাযোগ ঘটলে রিসেপ্টর-এর গঠন পাল্টে যায়। শুধু হরমোন-এর সাথে সংযুক্ত বেরিয়ে থাকা অংশটার গঠন নয়, কোষের ভিতর গেঁথে থাকা বাকি অংশটাতেও পরিবর্তন আসে।
এই পরিবর্তনটা কোষের কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস অব্দি পৌঁছয় কিভাবে? কোষের ভিতরের প্রোটিনগুলো তখন অবস্থান, স্থায়িত্ত্ব কিংবা গঠন পাল্টে একে অপরের সাথে জুড়ে যেতে পারে। এরকমভাবে জুড়ে বার্তা বহনের একটা পথ (signalling pathway) তৈরী করে ফেলতে পারে। একদম “রিলে রেস”-এর মতো, পরস্পর-সংযুক্ত প্রোটিন-এর শৃঙ্খল নিউক্লিয়াস-এর কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয় যে একটা রিসেপ্টর সক্রিয় হয়েছে। প্রত্যেকটা বার্তাবহ পথ আলাদা আলাদা ধরণের প্রোটিন ব্যবহার করে, বার্তা বহনের “কৌশল”-ও আলাদা, যদিও তাদের অন্তিম লক্ষ্য একই। এই বার্তাবহন পদ্ধতিতে নানা রকমের নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসবৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে। কোষে চালান হওয়ার সময় একটা সিগনাল স্তিমিত হয়ে যেতে পারে। আবার তার ক্ষমতা বেড়েও যেতে পারে যদি একটা প্রোটিন একসাথে অনেকগুলোকে সক্রিয় করে। এই চালানের সময় বাড়াকমাটাকে বোঝার একটা মজার উপায় নরমান রকওয়েল-এর যাত্রাপালা The Gossips-এ পাওয়া যায়। রকওয়েল এখানে দেখাচ্ছে কিভাবে একটা গুজব কানাঘুষোয় একজনের থেকে আরেকজনে ছড়ায়। যখন গুজবটা শুরুর ব্যক্তির কাছে ফিরে এলো, সেটা মাঝপথে এতটাই পাল্টে গেছে যে সে ব্যক্তি আর সেটাকে চিনতেই পারছেনা।

একটা কোষ প্রতিবেশী কোষের থেকে বার্তা পায় তার বাইরের জগতের মধ্যে দিয়ে। একটা লম্বা প্রোটিন-শৃঙ্খল এই বার্তাকে বাইরের কোষীয় মেমব্রেন থেকে কেন্দ্রের নিউক্লিয়াস-এ পৌঁছে দেয়, যাতে সেখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিন-এর প্রকাশ ঘটতে পারে। এই প্রোটিন শৃঙ্খল অনেকটা একটা “বালতিবাহক বাহিনী”-র (bucket brigade) মতো কাজ করে। এখানে, একটা ইম্প্রভ নাটকগোষ্ঠী (Playback theatre) এইরকম একটা বাহিনীকে দেখাচ্ছে। অভিনেতারা একটা কাল্পনিক বস্তুকে নিয়ে একে অপরের মধ্যে চালান করছে, কিন্তু চালানকালে সেই বস্তুটাকে কিছুটা পাল্টেও ফেলছে (B. Shilo, Cambridge, Massachussetts)।
জেনেটিক স্ক্রিন-এ এই বার্তাবহ পথগুলো আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীদের জন্য আরো দুটো চমক অপেক্ষা করে ছিল। প্রথমত, তারা দেখলেন যে ভ্রূণ বৃদ্ধির সময় কোষেদের মধ্যে যোগাযোগ গুটিকয়েক বার্তাবহ পথেই সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে পাঁচটা পথ প্রধান এবং বারেবারে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে তাদের ব্যবহার হয়, আরও তিনটে আছে যারা তুলনায় কম ব্যবহৃত। প্রত্যেকটা পথের উপাদান আলাদা, আণবিক স্তরে কর্মপদ্ধতি আলাদা। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই মেমব্রেন পেরিয়ে নিউক্লিয়াস-এ তথ্য পৌঁছে দেয় যাতে জিন-এর প্রকাশের (gene expression) ধরণকে বদলানো যায়।
দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে এই পথগুলো বিবর্তনের মাঝে পড়েও একই রয়ে গেছে (highly conserved in evolution)। সরল জটিল সব রকম জীবেই এদের দেখা যায়। এর মানে হলো, সব বহুকোষী প্রাণীর মধ্যেই কোষগুলো একই ভাষা ব্যবহার করে কথপোকথন করতে। এই ভাষা গোটা বিবর্তন ধরে তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও একই ছিল। এই বার্তাবহ পথগুলো সবেতেই সমান, সে নেমাটোড কৃমি হোক কি মাছি, কি মানুষ। এই আবিষ্কারটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধরণধারণ পাল্টে দিল। আগে ছোট ছোট বিজ্ঞানীর গোষ্ঠী আলাদা আলাদা জীব নিয়ে নাড়াচাড়া করতো, একে অপরের কাজের মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিল না। হঠাৎ দেখা গেল যে ওমা, সবাই আসলে একই আণবিক যোগাযোগব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছে! ফলের মাছির চোখের ক্রমবিকাশ আর মানুষের দেহে ক্যান্সার, এরকম সম্পূর্ণ আলাদা কিছু প্রক্রিয়া একদম একই যন্ত্রের ব্যবহার করছে। এই যে বার্তাবহনের সার্বজনীন চরিত্র, এটা জীববিজ্ঞানের জগতে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনলো। বিশেষ কোনো একটা জীবের জগতে সংকীর্ণ না থেকে বিজ্ঞানীরা অনেক ব্যাপক একটা পন্থা অবলম্বন করতে পারলেন।
(‘Life’s blueprint’ বইটা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছে ‘বিজ্ঞান’ টীম-এর অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং কুণাল চক্রবর্তী।)