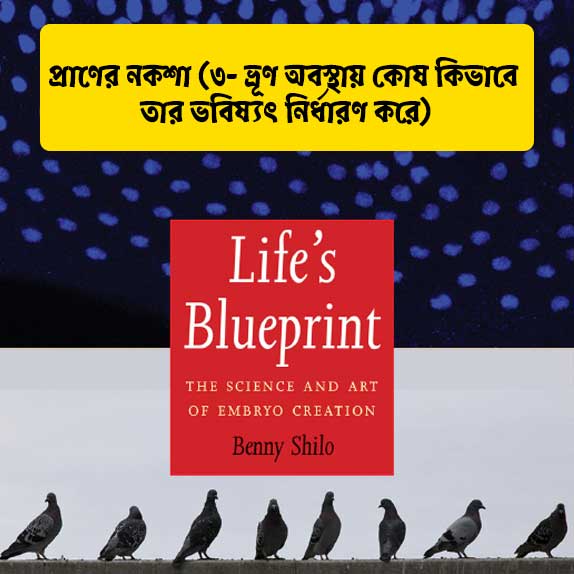নিচের পোস্ট-টা মলিকুলার জেনেটিক্স গবেষক বেনি শিলো-র লেখা ‘Life’s Blueprint’ বইটার তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ। বইটা সম্বন্ধে আরো জানতে ভূমিকাটি দেখুন।
সেই অ্যারিস্টট্ল-এর সময় থেকে, মানে প্রায় দু’হাজার বছরেরও আগে থেকে কিছু সময় আগে পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল যে ভ্রূণের বৃদ্ধি আগে থেকেই নির্ধারিত। শুধু ভ্রূণই নয়, সেই নিষেকেরও আগে থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ জীবদেহের পরিণতি, সব আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। ভ্রূণ শুধুমাত্র আকারে বড়ো হয়ে জীবদেহ তৈরী হয়। এই পূর্বনির্ধারণের তত্ত্বটা খানিকটা এরকম যে, শুক্রাণু অথবা ডিম্বাণুর মধ্যেই একটা গোটা মানুষ রয়েছে, শুধু আকারে ছোটো, এই যা। এই ছোটো আকারের মানুষকে বলা হতো হোমাঙ্কুলাস (homunculus)। সতেরোশো শতাব্দীর শেষের দিকে যখন মাইক্রোস্কোপে শুক্রাণু দেখা সম্ভব হলো, সেই সময়ের অনেক গবেষকই তার মধ্যে হোমাঙ্কুলাস দেখতে শুরু করে দিয়েছেন। নিকোলাস হার্টশোকার-এর মতো গবেষকরা তো একদম হোমাঙ্কুলাস এঁকেই ফেললেন। তখনো আধুনিক জেনেটিক্স-এর জন্ম হয়নি। এই হোমাঙ্কুলাস তত্ত্বে একটা সমস্যা ছিল। যদি বাবা মা একজনের থেকেই সব নির্ধারিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে মোটেই এটা স্পষ্ট হয় না যে পরিণত সন্তানের দেহে বাবা মা দুজনেরই প্রভাব কিভাবে পড়ে।
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভ্রূণবিদরা যখন ভ্রূণ নিয়ে নাড়াচাড়া করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন, তখন তাঁরা একটাই প্রশ্নে মন দিলেন। ভ্রূণের প্রত্যেকটা কোষের পরিণতি কি আগে থেকেই ঠিক হয়ে রয়েছে নাকি ভ্রূণের একটুখানি টুকরো কেটে নিয়ে তার থেকে আবার একটা পুরো ভ্রূণ তৈরী করা সম্ভব। নানা রকমের পদ্ধতি ব্যবহার করে তাঁরা ভ্রূণের থেকে বিভিন্নভাবে নেওয়া অংশবিশেষের বৃদ্ধি দেখা শুরু করলেন।
এরকম একটা পরীক্ষার উদাহরণ দি। একটা দ্বিকোষী সামুদ্রিক আর্চিনের ভ্রূণ নিয়ে একটা কোষকে গরম ছুঁচ ফুটিয়ে মেরে ফেলা হলো, আর তারপর দেখা হলো যে তার থেকে আবার গোটা ভ্রূণ তৈরী হয় নাকি সেই বেঁচে থাকা একটা কোষ থেকে শুধু অর্ধেক ভ্রূণই বেড়ে চলে। আরেক রকম পরীক্ষা হলো একটা ভ্রূণ থেকে সব কোষগুলো আলাদা করে নেওয়া, তারপর দেখা যে সেই আলাদা করে নেওয়া কোষ থেকে আবার একটা গোটা ভ্রূণ তৈরী হয় কিনা। গবেষকরা একেক সময় একেক ফল পেলেন। কখনও দেখা গেল যে একটা গোটা ভ্রূণ তৈরী হলো না, আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেল যে গোটা একটা ভ্রূণ তৈরী হলো বটে কিন্তু আকারে সেটা খানিকটা ছোট। হান্স স্পিমান তাঁর নিজের ছোট্ট মেয়ের মাথার চুলের সাহায্যে একটা উভচরী জীবের ভ্রূণের “দ্বি-কোষী” দশায় দুটো কোষ আলাদা করতে পেরেছিলেন। তিনি দেখলেন যদি একটা বিশেষ তল বরাবর কোষগুলোকে আলাদা করা যায় তাহলে একটা কোষ থেকেই আবার একটা গোটা ভ্রূণ তৈরী সম্ভব ।
পূর্বর্নির্ধারণের তত্ত্ব (preformation theory) ভুল, অর্থাৎ ভ্রূণের বৃদ্ধি আগে থেকে সব ঠিক করা আছে এটা সত্যি নয়। ভ্রূণের কিছু অংশ থেকে আবার গোটা ভ্রূণ তৈরী সম্ভব।
এই পরীক্ষার ফলগুলো এটাই প্রমাণ করলো যে, পূর্বর্নির্ধারণের তত্ত্ব (preformation theory) ভুল, অর্থাৎ ভ্রূণের বৃদ্ধি আগে থেকে সব ঠিক করা আছে এটা সত্যি নয়। ভ্রূণের কিছু অংশ থেকে আবার গোটা ভ্রূণ তৈরী সম্ভব। ১৯২৪-এ স্পিমান এর ল্যাবরেটরিরই একজন পি এইচ ডি ছাত্রী হিল্ডে মানগোল্ড এমন একটা ঐতিহাসিক পরীক্ষা করেছিলেন যে তার থেকেই সূচনা হয় আধুনিক জীববৃদ্ধি বিজ্ঞানের (modern developmental biology)। মানগোল্ড একটা গোসাপের মতো উভচরী জীবের (newt) ভ্রূণের একটা বিশেষ জায়গা থেকে কায়দা করে একটুখানি কোষ পিন্ড আলাদা করে নিয়েছিলেন। ওই জায়গার কোষগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো যে ওখান থেকেই ব্যাঙাচির মতো লার্ভার মাথা আর মেরুদন্ড তৈরী হয়। তারপর সেই আলাদা করা কোষপিন্ডকে বসিয়ে দিলেন অন্য আর একটা ভ্রূণের ঘাড়ে। দেখা গেলো যে ওই কোষপিন্ডটা দ্বিতীয় ভ্রূণটার একটা অংশ হয়ে গেল। কোন অংশটা কার সেটা আলাদা করে বোঝার সুবিধের জন্য মানগোল্ড দ্বিতীয় ভ্রূণটার কোষগুলোকে একটা রং দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন আর যে কোষপিন্ডটা বসিয়েছিলেন, সেটা ছিল সাদাটে।
এই কাটাকুটি আর জোড়াজুড়ির পদ্ধতিটা খুব যে নিপুণ ছিল তা নয়, বরং বেশ গোদাটেই ছিল, তাই নব্বইয়ের এর বেশি প্রতিস্থাপন করেও সাফল্য জুটেছিল গুটি কয়েকবার। কিন্তু ওই সামান্য সাফল্যই এতো আশ্চর্যের ছিল যে ওখান থেকেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আধুনিক জীববৃদ্ধি বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়। দেখা গেল যে, এই প্রতিস্থাপন ধারক কোষগুলোকে বাধ্য করলো গায়ে গায়ে জোড়া যমজের (Siamese twin) পরিণতিতে, যার মাথাও জোড়া আবার মেরুদন্ডও জোড়া। এই জোড়গুলো এতটাই ভালো যে একজনকে অন্যজনের থেকে আলাদা করা দায় (নিচের ছবি দেখো)|

উপরের ছবি : ভ্রূণ প্রতিস্থাপন পরীক্ষা (H. Kuroda and E. De Robertis, University of California, Los Angeles, and Howard Hughes Medical Institute)
নিচের ছবি : নিউ হ্যাম্পশায়ার-এ শরৎকালের একটা রাস্তা দুভাগ হয়ে যাচ্ছে। এইবার কোনদিকে যাবে? ( Benny Shilo)
যুক্তির খাতিরে বলাই যায় যে এটা আদৌ আশ্চর্যের নয়। কোষ পিন্ডগুলো থেকে মাথা তৈরী হতো, সেটাই হয়েছে, তা অন্য একটা ধড়েই হোক না কেন। কিন্তু প্রতিস্থাপিত কোষপিন্ড আর ধারক ভ্রূণের কোষগুলো রঙের জন্য আলাদা করে চেনা সম্ভব ছিল। অবাক কান্ড হলো যে দুটো মাথার মধ্যে বেশিরভাগ কোষ এসেছে ধারকের থেকে। অন্যভাবে বললে, প্রতিস্থাপিত কোষগুলো পরিচালকের (organizer) ভূমিকা নিয়েছে আর আশেপাশের গ্রাহক কোষগুলোকে প্রভাবিত (induce) করেছে এই নতুন দশায় আসতে। পরবর্তী কালে এই পরিচালনার ঘটনাকেই নাম দেওয়া হয়েছে স্পিমান অর্গানাইজার। স্পিমান এই ঘটনাটাকে নাম দিয়েছিলেন ইনডাকশন (induction) বা আবেশ। ভ্রূণের বৃদ্ধির ব্যাপারে আমরা আজ যতটুকু বুঝি তার মর্ম লুকিয়ে রয়েছে এই ইনডাকশন কথাটার মধ্যে। ভাবনাটা হলো এরকম, এক ধরণের কোষ তাদের প্রতিবেশী কোষেদের প্রভাবিত করে এবং অন্যধরণের টিসু বা কলা তৈরী করতে বাধ্য করে। তারা প্রতিবেশী কোষদের সাথে যোগাযোগ করে এমন নির্দেশ দেয় যে সেই কোষগুলোর রকমসকম যায় পাল্টে। কোষে কোষে যোগাযোগ হয় কিছু বিশেষ সংকেতের মাধ্যমে। এই সংকেত কতকটা কথা বলার মতো। কিছু কোষ কথা বলে নির্দেশ দেয় আর অন্য কিছু কোষ সেই কথা শুনে নির্দেশ পালন করে। গোড়াতে কোষগুলোর একাধিক বৃদ্ধির পথে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শেষমেশ কোন পথে যাবে, তা পুরোটাই নির্ভর করে তাদের মধ্যে সংকেতের আদান প্রদানের ওপর। অন্যভাবে বললে, জীব দেহের বৃদ্ধি এইরকম কোষে কোষে বাক্যালাপের মধ্যে দিয়েই হয়, যেখানে একটা কোষ তার প্রতিবেশী কোষেদের বিশেষীকরণে বাধ্য করে (cell differentiation)। তাই পুরো ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করতে হলে আমাদের বুঝতে হবে কিছু কোষ অন্য কোষেদের কাছ থেকে কি নির্দেশ পায় এবং সেই নির্দেশের ভিত্তিতে কিরকম পথ বেছে নেয় (নিচের ছবি দেখো)।
জীব দেহের বৃদ্ধি এইরকম কোষে কোষে বাক্যালাপের মধ্যে দিয়েই হয়, যেখানে একটা কোষ তার প্রতিবেশী কোষেদের বিশেষীকরণে বাধ্য করে (cell differentiation)।
এইটুকু বোঝার পর এক ঝাঁক নতুন প্রশ্নের উদয় হলো। এটা বুঝতে পারলাম যে, ভ্রূণবৃদ্ধির রহস্য উদ্ধার করতে হলে, কোষে কোষে যে কথা হয় তার ভাষা আমাদের বুঝতেই হবে। এছাড়াও কোষের সামাজিক আচরণ নির্ণয় করে যে নিয়মগুলো, সেগুলোর হদিশ আমাদের পেতে হবে। সেই নিয়মগুলো জানলে তবেই একটা ভ্রূণকে একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া যাবে।
স্পিমান আর মানগোল্ডের পরীক্ষার ফলে অনেকেই খুঁজতে লাগলো কারা ভ্রূণের ধারক কোষ আর মস্তিষ্কের কোষকে নির্দেশ দেয় দ্বিতীয় আর একটা মাথা তৈরী করতে। অনেক পরীক্ষাও হলো, কিন্তু ফল শুধুই হতাশা। প্রশ্নটা হলো, ওই নির্দেশগুলোতে কোন অণুগুলো অংশগ্রহণ করে? কোনো কোনো গবেষক দাবী করলেন যে ফোটানো টিসু বা কলা প্রতিস্থাপন করেও জোড়া মাথা তৈরী সম্ভব। এর মানে হলো, যে জিনিসটা ওই নির্দেশ দিচ্ছে সেটা গরম করলেও নষ্ট হয় না। অন্যরা আবার দেখালেন যে ধারক কোষের মধ্যে ব্যবধান থাকলেও আগের মতোই সেগুলো মস্তিষ্কের কোষে পরিণত হচ্ছে। তবে কি আদৌ আবেশ কিংবা কোষে কোষে যোগাযোগের কোনো প্রয়োজনই নেই? স্পিমান আর মানগোল্ডের পরীক্ষা যতই পথপ্রদর্শক হোক না কেন, সেই পরীক্ষার রহস্য উদ্ধার করতে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। কারণ ভ্রূণের অন্তিম দশা যারা নির্ণয় করে, সেই কোষে কোষে কথার ভাষা বোঝার উপায় গবেষকদের কাছে অনেকদিন পর্যন্ত ছিল না।
১৯৮০-র দশকে মলিকুলার বায়োলজির নতুন পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে এটা দেখানো গেলো যে শুধুমাত্র পরিচালক কোষের অঞ্চলেই কিছু বিশেষ জিনের প্রকাশের ফলে নির্দিষ্ট কিছু আরএনএ অণু তৈরী হয়। অর্থাৎ,আণবিক গঠনের দিক থেকে দেখলে ওই অঞ্চলটার একটা আলাদা সত্ত্বা রয়েছে।
এরপর ১৯৯০-র গোড়ায় কিছু গবেষণা থেকে জানা গেলো যে ওই অঞ্চলে শুধু যে কিছু বিশেষ জিনের প্রকাশ ঘটে তা নয়, তার থেকে প্রোটিন তৈরী হয়ে নিঃসৃত হয় কোষের বাইরে, অতএব তারা প্রতিবেশী কোষেদের প্রভাবিত করতে পারে।
সময়ের সাথে সাথে মলিকুলার বায়োলজিতে নতুন প্রযুক্তির উদয় হলো, কিছু উত্তরেরও আভাস পাওয়া গেল। ব্যাঙের ভ্রূণ বৃদ্ধির সময় সেই নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্পিমান অর্গানাইজার-এর আবেশের ক্রিয়াপদ্ধতি বোঝা সম্ভব হলো। মোটামুটি ধারণাটা ছিল এইরকম যে পরিচালক কোষগুলো প্রতিবেশী কোষেদের থেকে আলাদা এবং তাদের মধ্যে কিছু বিশেষ জিন প্রকাশিত হতে পারে। ফলে, সেখানে কিছু নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরী হয় আর এই প্রোটিনগুলো আশেপাশের কোষেদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। ১৯৮০-র দশকে মলিকুলার বায়োলজির নতুন পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে এটা দেখানো গেলো যে শুধুমাত্র পরিচালক কোষের অঞ্চলেই কিছু বিশেষ জিনের প্রকাশের ফলে নির্দিষ্ট কিছু আরএনএ অণু তৈরী হয়। অর্থাৎ,আণবিক গঠনের দিক থেকে দেখলে ওই অঞ্চলটার একটা আলাদা সত্ত্বা রয়েছে।
এরপর ১৯৯০-র গোড়ায় কিছু গবেষণা থেকে জানা গেলো যে ওই অঞ্চলে শুধু যে কিছু বিশেষ জিনের প্রকাশ ঘটে, তা নয়। তার থেকে প্রোটিন তৈরী হয়ে নিঃসৃত হয় কোষের বাইরে, অতএব তারা প্রতিবেশী কোষেদের প্রভাবিত করতে পারে। তবে কি সত্তর বছর আগে স্পিমান যে যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা আন্দাজ করেছিলেন, এই প্রোটিন অণুগুলোই কি সেই যোগাযোগ সম্পন্ন করে? স্পিমান কলা বা টিসু প্রতিস্থাপন করে যে ফল পেয়েছিলেন, বিজ্ঞানীরা ওই সম্ভাব্য অণুগুলো প্রতিস্থাপন করে একই ফল পেলেন। এর ফলে এটা জোর দিয়ে বলা গেল যে এই অণুগুলোই পরিচালক কোষের ধর্ম নির্ধারণ করে, যে ধর্ম স্পিমান আর মানগোল্ড-এর সেই প্রথম চমকে দেওয়া পরীক্ষায় দেখা গেছিলো।
ওই অণুগুলোর ধর্ম কি? যেহেতু সত্তর বছর ধরে বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ পেয়েছেন, আমরা পিছন ফিরে দেখতে পারি কি ধরণের মনস্তত্ত্ব তাদের ধারণা কিংবা ভবিষ্যদ্বাণীকে প্রভাবিত করে । আবার বলি, আমরা এমন কিছু অণু নিয়ে নাড়াঘাঁটা করছি যা মাথার এবং ভিতরের মস্তিষ্কের গঠনের জন্য দায়ী। আমরা নিজেদের মস্তিষ্কের কথা মাথায় রেখে স্বাভাবিকভাবেই স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপকে বিশেষীকরণের উচ্চতম ধাপ হিসেবে দেখি, তা সেটা গোসাপের (newt) মধ্যেই হোক না কেন। এটা আঁচ করা যেতেই পারে যে মস্তিষ্কের গঠনের জন্য অত্যন্ত জটিল সব নির্দেশাবলীর প্রয়োজন হয় ।
যখন বৃদ্ধির সময় একটা কোষের সামনে দুটো রাস্তা খোলা রয়েছে। কোষের মধ্যে যে প্রাথমিক নির্দেশ রয়েছে তাতে সে বাঁধা গতে এগিয়ে একধরণের কোষ তৈরী করতে পারে, প্রায় গাড়ির “অটোপাইলট” মোড-এর মতো। অন্যদিকে, যদি সেই কোষ তার প্রতিবেশী কোষেদের থেকে নতুন কোনো নির্দেশ পায়, সে রাস্তা পাল্টে অন্য আর এক ধরণের কোষ তৈরী করতে পারে।
খুব সহজ একটা ঘটনা ধরা যাক, যখন বৃদ্ধির সময় একটা কোষের সামনে দুটো রাস্তা খোলা রয়েছে। কোষের মধ্যে যে প্রাথমিক নির্দেশ রয়েছে তাতে সে বাঁধা গতে এগিয়ে একধরণের কোষ তৈরী করতে পারে, প্রায় গাড়ির “অটোপাইলট” মোড-এর মতো। অন্যদিকে, যদি সেই কোষ তার প্রতিবেশী কোষেদের থেকে নতুন কোনো নির্দেশ পায়, সে রাস্তা পাল্টে অন্য আর এক ধরণের কোষ তৈরী করতে পারে। এই যদি দুটো পথ হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতেই পারছো বিজ্ঞানীরা কেন ভড়কে গেলেন যখন দেখলেন যে স্পিমান অর্গানাইজার-এর অণুগুলো নতুন পথে পরিচালনা করে না, বরং অন্য পথে যেতে বাধা দেয়। আরেকভাবে বললে, ওই অণুগুলো একটা কোষকে আশেপাশের কোষের সংকেত উপেক্ষা করিয়ে মাথা তৈরীর কাজে নামিয়ে দেয়, যেন সেটাই তার ভবিতব্য ছিল। আর যে কোষগুলো এই দমনকারী সংকেত পায় না, তারা অন্য অণুর নির্দেশে ধরাবাঁধা পথ ধরে পূর্বনির্দিষ্ট অঙ্গ তৈরী করে। এক্ষেত্রে যেমন ব্যাঙাচির পেট তৈরী হয়।
এর মানে কি গোসাপের ভ্রূণর কোষগুলো কোনো বাইরের নির্দেশ ছাড়াই মাথা আর মস্তিষ্ক তৈরী করতে পারে? মোটেই না। এটা ভাবা ভুল নয় যে মস্তিষ্কের মতো জটিল অঙ্গ তৈরী করতে গেলে কোষকে অনেক নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মেনে চলতে হয়। কিন্তু এর সাথে স্পিমান অর্গানাইজার-এর দমনকারী ভূমিকাকে মেলাবো কি করে ? আসলে একটা কোষ পরপর ধাপেধাপে নির্দেশ মেনে সিদ্ধান্তের পর সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে চলে। এই নিয়ে পরে আরো বিস্তারিত বলবো, তবে মোদ্দা কথা হলো, প্রত্যেক সিদ্ধান্তের আগে কোষের কাছে যে রাস্তাগুলো খোলা থাকে, সেগুলো খুবই সুস্পষ্ট, তবে তার থেকে শেষ অবস্থাটা নির্ণয় করা যায় না। এরকম অনেক সিদ্ধান্ত মিলে তবে একটা কোষ থেকে নানা ধরণের বিশিষ্ট বিশিষ্ট কোষ তৈরী হয়ে জটিল অঙ্গের গঠন হয়। এটা অনেকটা গাড়ি চালিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়ার মতন। প্রথম বাঁক নেওয়ার সময়, আপনি গন্তব্যস্থলের ঠিকানা নিয়ে ভাবছেন না, শুধু কোন দিকে সেইটা রয়েছে, সেটা মাথায় রেখে আন্দাজমতো বাঁক নিচ্ছেন।।
একটা কোষ থেকে মাথা তৈরী হবে না পেট তৈরী হবে সেটা নির্ভর করে কোষের একদম প্রথমে নেওয়া সিদ্ধান্তের ওপর। এই প্রথম ধাপেই, একটা কোষকে মাথা তৈরির দিকে ঠেলে দেওয়া যায় স্রেফ বিকল্পটাকে দমন করে দিয়ে।
যদিও একটা কোষের প্রথম সিদ্ধান্তটা খুব গোদা, তার গুরুত্ব কিন্তু সবচেয়ে বেশি। একটা কোষ থেকে মাথা তৈরী হবে না পেট তৈরী হবে সেটা নির্ভর করে কোষের একদম প্রথমে নেওয়া সিদ্ধান্তের ওপর। এই প্রথম ধাপেই, একটা কোষকে মাথা তৈরির দিকে ঠেলে দেওয়া যায় স্রেফ বিকল্পটাকে দমন করে দিয়ে। একবার মোটামুটি মাথা তৈরীর একটা জায়গা নিদিষ্ট হয়ে গেলে, পরের সিদ্ধান্তগুলো সেই মাথার অন্তিম গঠনের সূক্ষ্ম নকশাগুলো নির্ণয় করে। সত্যি বলতে কি, এখানে কিন্তু বাইরের সংকেত না পেলে উপায় নেই। প্রচুর সুপরিচালিত এবং সুসংগঠিত কার্যকলাপ ঘটলে তবেই মাথা বা চোখের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গঠন তৈরী সম্ভব।
(‘Life’s blueprint’ বইটা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছে ‘বিজ্ঞান’ টীম-এর কুণাল চক্রবর্তী এবং অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়।)