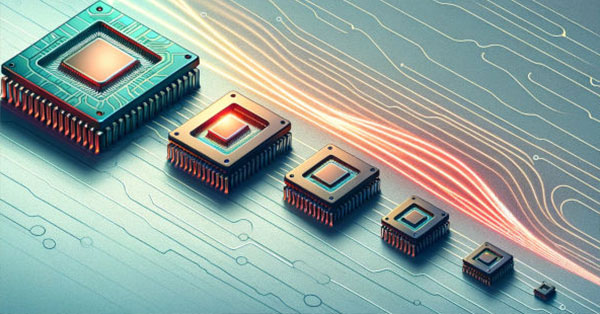রাজীবুল: আমরা যখন নতুন কম্পিউটার বা ফোন কিনতে যাই, এই বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে: ‘নেক্সট জেনারেশন চিপ’। এই চিপ, ওই চিপ, এবং সেটা পাল্টাতেই থাকে। আমাকে এটা বল, আমার নতুন কম্পিউটারে যে চিপটা রয়েছে, সেটার মডেলটা হয়তো গত এক বছরে ফাইনাল হয়েছে, কিন্তু এরকম একটা চিপের পিছনে কত বছরের গবেষণা থাকে? মোটামুটিভাবে বললেই হবে।
দেবলীনা: সেটা নির্ভর করে কতটা পরিবর্তন তুই আনছিস, তার উপর। অর্থাৎ, চিপের আগের সংস্করণের সাথে এইটা কতটা আলাদা। যত বেশি পরিবর্তন আনতে চাইবে, তত বেশি সময় লাগবে। একদম গোড়া থেকে শুরু করতে চাইলে অন্তত পাঁচ বছর সময় লাগবে।
পাঁচ বছরের গবেষণা লাগবে?
হ্যাঁ, যদি একদম গোড়া থেকে শুরু করা হয়, সেরকমই লাগবে। সেই কারণেই ব্যবসার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বলা হয়, একটু একটু করে পরিবর্তনগুলো করো (incremental changes)।
মানে স্পিড একটু বাড়ানো হলো, বা সেরকম কিছু?
হ্যাঁ, একটু উন্নতি হলো, কিন্তু একদম গোড়া থেকে শুরু করা হয়নি।
আচ্ছা এই যে পাঁচ বছরের সাইকেলের কথা বললি — যেটা শুরু হয় নতুন চিপ বাজারে আসার পাঁচ বছর আগে থেকে — সেই প্রসেসটা কী রকম? পাঁচ বছর ধরে কী হয়? কতজন মিলে কাজটা করে? সেইটা যদি একটু বলিস খুব ভালো হয়।
এটা একটা অনেক বড় collaborative প্রোজেক্ট হয়। অন্তত দশ হাজার ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিসিয়ান এবং সিনিয়র থেকে জুনিয়র বিভিন্ন লেভেলের সায়েন্টিস্ট বা গবেষক, এমনকি ডিরেক্টরও এর সাথে যুক্ত থাকেন। একদম গোড়ার দিকে ‘ডিফেক্ট ডেনসিটি’ (defect density) অনেক বেশি থাকে। আস্তে আস্তে পদ্ধতিটা যত পরিণত হয়, এই ‘ডিফেক্ট ডেনসিটি’-টা কমতে থাকে।
নতুন চিপ ডিজাইনে এই দুটো ব্যাপারকেই খেয়াল রাখতে হয়: ‘ডিফেক্ট ডেনসিটি’ এবং ‘পারফরমেন্স’
‘ডিফেক্ট ডেনসিটি’ মানে আমি যতগুলো চিপ বানাচ্ছি, তার মধ্যে কতগুলো ঠিকঠাক তৈরি হচ্ছে আর কতগুলো ফেল করছে?
হ্যাঁ। তার সাথে আরেকটা জরুরি ব্যাপার হলো ‘পারফরমেন্স’ (performance)। অর্থাৎ, বাজারে যে চিপটা বিক্রি হচ্ছে, তার থেকে ভালো ‘পারফরমেন্স’ তো তোমাকে দিতেই হবে। তুমি যতই ভিতরের কলকব্জা পাল্টাও (architecture change), আগের থেকে ভালো না হলে তো কেউ কিনবে না। তাই একটা নতুন চিপ ডিজাইনে এই দুটো ব্যাপারকেই খেয়াল রাখতে হয়: ‘ডিফেক্ট ডেনসিটি’ এবং ‘পারফরমেন্স’।
এই যে দশ হাজার বিজ্ঞানী আর ইঞ্জিনিয়ার-এর টিম, এদের শিক্ষাগত দিক থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কী? এরা কী নিয়ে পড়াশোনা করে এসেছে?
অনেকেই ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার, কেউ কেউ পদার্থবিদ, কেউ কেউ অঙ্ক নিয়ে পড়েছে, কেউ কেউ কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ার। বিভিন্ন বিষয় থেকে তারা উঠে আসে।
সকলেই পিএইচডি?
সকলেই পিএইচডি।
ধরা যাক, এই দশ হাজার গবেষক ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে কাজটা চলছে। এখন, এই দশ হাজার লোক তো একটা সেমিনার রুমে বসে আলোচনা করতে পারবে না। নিশ্চয় কিছু বিভাগ আছে। বিভাগগুলো কীভাবে হয়? ধর, তুই যে বিভাগে কাজ করিস, তোর সাথে কি ইঞ্জিনিয়ার-ও কাজ করে, গণিতজ্ঞ-ও কাজ করে? নাকি এক বিষয় থেকে উঠে আসা লোক একসাথে কাজ করে — সব পদার্থবিদ একসাথে, ইঞ্জিনিয়ার একসাথে, এইরকম? কীভাবে হয় ব্যাপারটা?
ছোট ছোট টিম-এ ভাগ করা থাকে। ধর, দশজনের টিম একটা বিশেষ অংশ নিয়েই কাজ করবে। ওটাই তাদের শেষমেশ তৈরি করে দিতে হয় (deliverable)।
এবং সেই টিম-এ সব বিষয় থেকে উঠে আসা লোক মিলিয়ে মিশিয়ে থাকে?
মিলিয়ে মিশিয়ে থাকে। যেমন প্রয়োজন পড়বে, সেইমতো টিম-টা বেড়ে উঠবে।
সেরকম করে পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন ধাপ সম্পূর্ণ করে তবে গিয়ে আমরা শেষের চিপটা পাই। আমরা যখন বলি, ‘নতুন মডেল-টা আসছে, সেটা একটা নেক্সট জেনারেশন চিপ’, তার পিছনে এতজন বিজ্ঞানীর এতদিনের কাজ থাকে?
হ্যাঁ। ধর যদি দশ বছর লাগে, তাহলে একেকজনের জীবনের একটা বড় অংশ এর পিছনেই গেল।
সিলিকন-এর পরিবর্তে হয়তো আরো উন্নত পদার্থ এসে যাবে, যেখানে বৈদ্যুতিক সচলতা (electrical mobility) আরো বেশি হবে বা কিছু। কিন্তু সেরকম কোনো পদার্থ ব্যবহার করা ভীষণ খরচসাপেক্ষ।
আমরা যখন সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে পড়েছি, সেমিকন্ডাক্টর বলতে প্রথমেই মাথায় আসে সিলিকন (silicon)। আমাদের বাবা দাদুরা যখন পড়তেন, তারাও সিলিকন-এর কথাই পড়ে এসেছেন। এখনো কি সিলিকন নিয়েই কাজ হয় নাকি অনেক কিছু হয়ে গেছে তারপর?
এটা খুব ভালো প্রশ্ন। আমারও ধারণা ছিল যে সিলিকন-এর পরিবর্তে হয়তো আরো উন্নত পদার্থ এসে যাবে, যেখানে বৈদ্যুতিক সচলতা (electrical mobility) আরো বেশি হবে বা কিছু। কিন্তু সেরকম কোনো পদার্থ ব্যবহার করা ভীষণ খরচসাপেক্ষ। তাই জন্যে হয়তো এটা কোনোদিনই হবে না।
300 মিমি সাইজের ওয়েফার, যাতে কোনো ত্রুটি নেই, এরকম বানাতে সিলিকন-এর কোনো বিকল্প আমাদের কাছে নেই। আর যদি সেরকম বানাতেও হয়, সেটা MBE চেম্বার বা এরকম কিছুতে বানাতে হবে। সেটা খুব খরচসাপেক্ষ হয়ে যাবে। খেয়াল রাখিস যে এই ওয়েফার বানাতে হয় ব্যাপক হারে (large scale)। একেকটা কারখানা থেকে সপ্তাহে পাঁচ-দশ হাজার ওয়েফার বেরোয়। অতএব এর জন্য ব্যাপক হারে পদার্থের সাপ্লাই থাকতে হবে।
এছাড়া যন্ত্রপাতির কথাও ভাবতে হবে। একেকটা সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব্রিকেশন প্ল্যান্ট (সংক্ষেপে fab) বানাতে 20 বিলিয়ন ডলার অব্দি লাগে। সেখানকার যন্ত্রপাতিগুলো সিলিকন-এর কথা ভেবে কেনা হয়েছে। সেই যন্ত্রপাতিগুলোকে হঠাৎ করে পাল্টানো অত সহজ নয়।
এখনো অব্দি তাহলে সিলিকন নিয়ে কাজ চলছে। মাঝখানে আমরা গ্যালিয়াম আর্সেনাইড বা জার্মেনিয়াম, এই জাতীয় সেমিকন্ডাক্টরের নাম শুনেছিলাম। কিন্তু সেগুলো কোনোটাই সিলিকন-এর জায়গায় আসতে পারেনি।
একটা চেষ্টা আমরা করেছিলাম সিগি (Si-Ge) নিয়ে। তাইওয়ান-এর TSMC কোম্পানি বা আমাদের ইন্টেল-এও চেষ্টা হয়েছিল। তবে তুই বললি বলে মনে পড়লো সেটার কথা।
আমি যদি একটু ভবিষ্যতের দিকে যাই, চিপগুলো ছোট হতে হতে 4 ন্যানোমিটার অব্দি —
3 বা 2 ন্যানোমিটারও হয়েছে।
আচ্ছা, 3 বা 2-এ নেমে গেছে সাইজ। তো এখন থেকে আমি যদি দশ-কুড়ি বছর বাদে দেখি, তোর কি মনে হয় — ইন্ডাস্ট্রি-টা কোনদিকে যাচ্ছে?
এটা ভীষণ ভালো প্রশ্ন। ছোট করতে করতে তো 3 বা 2-এ এসে গেছি, তোর মনে হতেই পারে — এবার কী হবে?
তখন হয়তো আর্কিটেকচার (architecture) পাল্টাতে হবে। এখন যেমন আমরা ন্যানোওয়্যার (nanowire) নিয়ে কাজ করি, এরপর হয়তো কোয়ান্টাম ডট-এর (quantum dot) দিকে যেতে হবে।
মানে সম্পূর্ণ নতুন প্রযুক্তির দিকে যেতে হবে। সেটার জন্য তো আবার নতুন যন্ত্রপাতি বানাতে হবে?
যন্ত্রপাতি হয়তো বানাতে হবে না। সিলিকন নিয়েই কাজ হবে। তবে হতে পারে আমরা আরো স্ট্যাকিং (stacking) করতে পারবো — অর্থাৎ একটার উপর আরেকটা এরকম অনেকগুলো বসাতে পারবো [1]।
তবে এই আলোচনা থেকে আশা করি বুঝতে পারছিস যে আমরা কী কী করতে পারি, সেটা অনেকগুলো গণ্ডির মধ্যে বাঁধা।
কী রকম গণ্ডি?
আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি বা গবেষণা করি, নতুন পদার্থ পেলে মনে হয়, নিশ্চয় এর কোনো প্রয়োগ বার করা যাবে। যেমন, টোপোলজিক্যাল ইনসুলেটর (topological insulator) বলে যে পদার্থটা হয়। আমাদের মনে হয়, এই পদার্থটাও হয়তো কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি সেটা কতটা চ্যালেঞ্জিং। অনেকগুলো শর্ত মেনে কাজ করতে হয়। তুই যে একটা নতুন সেমিকন্ডাক্টর তৈরির পদ্ধতি বানাবি, তোকে সেই শর্তগুলো মাথায় রাখতে হবে।
শর্তগুলো শুধু যে বিজ্ঞানের দিক থেকে আসে, তা নয়। ফান্ডিং-এর দিক থেকেও আসতে পারে।
কী পদার্থ ব্যবহার করা যাবে, তার কিছু বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে। বা যন্ত্রপাতির বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে। যন্ত্রপাতি খুব বেশি পাল্টে ফেলা যাবে না। এই সব গণ্ডি মেনে চলতে হয়।
প্রচ্ছদের ছবি: Dall-E
উৎসাহী পাঠকদের জন্য:
[1] Die stacking, EESEMI (link)
Video: