কৌশিকঃ নমস্কার, অধ্যাপক মহাদেবন! প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আমাদের সাথে বসার জন্য। আমি জানি, এই ইন্টারভিউটা আমাদের দেশের নওজোয়ান বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের খুব কাজে আসবে। অনেকেই হয়তো জানে না হার্ভার্ড-এর মত বড় জায়গাতে কীভাবে বিজ্ঞানচর্চা করা হয় এবং বিজ্ঞান নিয়ে কীভাবে ভাবনাচিন্তা করা হয়।
আচ্ছা, যদি আপনার ওয়েবসাইট দেখি, প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হলো আপনার কাজের ব্যাপ্তি। আপনি যেমন জৈব-অণুর গঠন এবং সেই গঠনের কার্যকারিতা নিয়ে ভেবেছেন, প্রাকৃতিক বিবর্তনে জ্যামিতির ভূমিকা নিয়ে ভেবেছেন, আবার প্রাণিজগতে সামাজিক আচরণ নিয়েও কাজ করেছেন। শুধু তাই না, দলাপাকানো কাগজের গঠন, কাগজ ভাঁজ করে অরিগামি বা ভাঁজ করে কেটে কিরিগামি, পতাকার হাওয়ায় দোলা, সকালের জলখাবারে দুধের মধ্যে কর্ন ফ্লেক্স-এর চলাফেরা, এই তালিকার তো শেষ নেই। আপনি পৃথিবীটাকে দেখেন কীভাবে? কোন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবেন, সেটা ঠিক করেন কী করে?
ড: মহাদেবনঃ (হেসে) আমাকে এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে বাধ্য করার জন্য ধন্যবাদ। আমার মনে হয়, বৈজ্ঞানিক সমস্যা খোঁজার সবথেকে ভালো উপায় হলো, পৃথিবীটাকে একটা শিশুর মত করে দেখা, একটা শিশুর ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা। যখন শিশুরা ছোট থাকে, প্রায় সবকিছু নিয়েই তাদের জিজ্ঞাসা থাকে। মনে হয় আমার ক্ষেত্রে, বড় হয়েও সেই জিজ্ঞাসা করার স্পৃহাটা হারিয়ে ফেলিনি।
এরপর প্রশ্ন হলো, কতরকমের তো জিজ্ঞাস্য আছে, কোনটার পিছনে ধাওয়া করা যায়? মনে রাখতে হবে, ব্যর্থতার ভয়ে থাকলে চলবে না। বেশিরভাগ সময়েই আমি ব্যর্থ হয়েছি। সে ঠিক আছে। বিজ্ঞান ব্যর্থতা মেনে নেয়, এমনকি ব্যর্থতায় উৎসাহ পায়, উৎসাহ পায় অনিশ্চয়তার মধ্যে। মনের মধ্যে অনিশ্চয়তা থাকলে তবেই না তুমি আরো গভীরে যেতে, আরো বেশি সময় ধরে পড়ে থাকতে বাধ্য হবে।
একটা শিশুর মনও সেইভাবে কাজ করে। বেশির ভাগ সময়েই, একটা শিশুর জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে না। কয়েকসময় মিলে যায়, এবং এটা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সত্যি। গত চারশো বছরে কয়েকবার মাত্র আমরা পেয়েছি অল্পসংখ্যক মৌলিক সূত্র। তারপর দেখেছি যে সেই সূত্রগুলো বারেবারে ফিরে আসছে, বিভিন্ন জায়গায়, মাঝেমাঝে সামান্য পোশাক বদল করে, আবার মাঝেমাঝে প্রায় একইভাবে।
কতরকমের তো জিজ্ঞাস্য আছে, কোনটার পিছনে ধাওয়া করা যায়? মনে রাখতে হবে, ব্যর্থতার ভয়ে থাকলে চলবে না। বেশিরভাগ সময়েই আমি ব্যর্থ হয়েছি। সে ঠিক আছে। বিজ্ঞান ব্যর্থতা মেনে নেয়, এমনকি ব্যর্থতায় উৎসাহ পায়।
তাই, আমার পদ্ধতি নিয়ে যদি জিজ্ঞেস করো তাহলে বলবো, জানালা খুলে বাইরে চেয়ে আছি, তার থেকে কম বা বেশী কিছু করছি না। একসময় নির্জীব পৃথিবী নিয়ে মাথা ঘামাতাম, আজকাল সজীব পৃথিবী নিয়ে পড়েছি।
আসলে আমরা পৃথিবীকে বুঝি কীভাবে, সেটা নিয়ে ভাবতেও আমার দারুণ লাগে। ধরো, পদার্থবিদ্যার তত্ত্বগুলো বোঝা মানে ঠিক কী? শুধু সমীকরণ দিয়ে বা গবেষণাগারে বোঝা নয়, একেবারে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বোঝা প্রয়োজন। আর অভিজ্ঞতা বলতে শুধু একজন ব্যক্তিসাধারণের আচরণের কথা বলছি না, হতে পারে সেটা সমষ্টিগত আচরণ। হতে পারে সেটা কোনো সামাজিক পোকামাকড়ের গোষ্ঠী, হতেও বা পারে মানুষের গোষ্ঠী। কেন একটা গোষ্ঠী বা দল একজন ব্যক্তিসাধারণের থেকে ভিন্ন আচরণ করে? বা কখন ভিন্ন আচরণ করে? এই সবকিছু নিয়েই আমার উৎসাহ রয়েছে।
খুব গুরুত্বপূর্ণ উত্তর! আচ্ছা, এই যে কৌতূহল-উদ্দীপক শিক্ষা (curiosity-driven learning) নিয়ে বললেন, শিক্ষাব্যবস্থায় এটা থাকা কি জরুরি?
আমার তো মনে হয়, আছে। অন্তত আশা করি, আছে। আমার মনে হয় আমরা সবাই জন্ম থেকেই কৌতূহলী। মাঝে মাঝে, যে কারণেই হোক, সেই কৌতূহলটা হারিয়ে ফেলি।
শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য কৌতূহলের আগুনটা জ্বালিয়ে রাখা। আর দ্বিতীয় লক্ষ্য সেই ছোট আগুনটা বড় করে তোলা। যুবসমাজকে সজীব আর নির্জীব জগত – দুই ব্যাপারেই কৌতূহলী করে তোলা। যুবসমাজ বলতে শুধু বয়েসের দিক থেকে বলছি না – যারা মন থেকে যুবক, আমি তাদেরকেও যুবসমাজের মধ্যেই রাখছি। যারা মনে করে পৃথিবীটাকে জানা দরকার, বোঝা দরকার। আর শিক্ষা যদি সত্যিই এই কৌতূহল জাগিয়ে রাখতে পারে, আমরা শিক্ষক হিসেবে খুব খুশী হব। আর সেটা করতে না পারলে বুঝতে হবে, গোড়ায় গলদ রয়েছে।
আমার মনে হয় আমরা সবাই জন্ম থেকেই কৌতূহলী। মাঝে মাঝে, যে কারণেই হোক, সেই কৌতূহলটা হারিয়ে ফেলি।
যদি বলি শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য নিজের সম্বন্ধে, বিশ্ব সম্বন্ধে জানা, তাহলে কেউ নিশ্চই আপত্তি করবে না। এই জানাটা কিন্তু কিছু হাসিল করার জন্যে নয়। খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যেরকম জানি, সেরকম করি। বিশ্বকে আরো ভালো করে জানলে আমাদের কাজগুলো বিশ্বপ্রকৃতির কল্যাণের স্বার্থে হবে, একে অপরের প্রতি আরো সদয় হবো আমরা। এই জানার ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অনেক গভীর প্রশ্ন আরেকটু ভালো বুঝতেও পারবো – যেমন আমরা কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাচ্ছি, পৃথিবী কী দিয়ে তৈরি, কীভাবে পৃথিবী চলছে, এইরম প্রশ্ন।
আপনি বললেন, বিশ্বের সাথে একাত্ম হওয়ার কথা। আপনার কাজগুলো যদি দেখি, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কোনো একটা মূল বিষয় নেই তার মধ্যে। মনে হয় অনেক রকম কাজের জগাখিচুড়ী। আপনি কীভাবে এতরকম বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পান? নাকি সেরকম কোনো যোগসূত্র নেই?
আমি পৃথিবীটাকে অঙ্ক আর পদার্থবিদ্যার চোখ দিয়ে দেখি। অঙ্কের চোখে দেখা মানে হলো পৃথিবীর জটিলতাকে কয়েকটা নিয়মে পর্যবসিত করা যায় কিনা, সেই সন্ধান করা। নিয়মগুলোকে আমরা বলি সূত্র। এখন এই সূত্রগুলোকে যে একেবারে তথাকথিত মৌলিক সূত্র হতে হবে, তার কোনো মানে নেই। (মৌলিক সূত্রর উদাহরণ হিসেবে আইনস্টাইন কি শ্রোয়েডিঙ্গার-এর সূত্র বলা যায়।) সেগুলো এমন সূত্রও হতে পারে যা অপেক্ষাকৃত জটিল অবস্থাকে অঙ্কের ভাষায় ধরতে পারে।
পদার্থবিদ্যা নিয়ে কাজ করি কারণ ওতেই আমার ট্রেনিং হয়েছে, কিছুটা ঘটনাচক্রে, কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবে। এই অঙ্ক আর পদার্থবিদ্যার মধ্যে কিন্তু ইচ্ছেমত এপার-ওপার করা যায়। দুইয়ে মিলে একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতিয়ার এসে যায় আমাদের হাতে: সেটা হলো বিবিধের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা। যে নিয়মটা এক জায়গায় দেখে আসছি, হঠাৎ করে সেটা শুরুর ক্ষেত্রের বাইরে খেটে যায়।
এইটা দেখে আমি এখনও হতবাক আর আপ্লুত হয়ে যাই। অবশ্যই এক জায়গার জিনিস অন্য জায়গায় খেটে গেলে সুবিধেও হয় তাতে। একই নিয়ম, একই সূত্র এই স্তরেও খাটে, ওই স্তরেও খাটে। অতএব এখানকার সব শিক্ষা ওখানে লাগাতে পারো।
অতএব তুমি যখন বললে, আমি আপাতদৃষ্টিতে অনেকরকম আলাদা আলাদা জিনিসের উপর কাজ করি, সেটা একদম ঠিক। আমি চেষ্টা করি বিশেষ কিছু ঘটনার বিশ্লেষণ করতে, এই আশায় যে সেগুলোর কিনারা করতে পারলে কিছু সাধারণ সূত্র বেরিয়ে আসবে। অঙ্কের ভাষায় সেই সূত্রগুলোকে ধরা যাবে।
আমি চেষ্টা করি বিশেষ কিছু ঘটনার বিশ্লেষণ করতে, এই আশায় যে সেগুলোর কিনারা করতে পারলে কিছু সাধারণ সূত্র বেরিয়ে আসবে। অঙ্কের ভাষায় সেই সূত্রগুলোকে ধরা যাবে।
ঠিক। শুধু পদার্থবিদ্যার মধ্যেই আপনি কাজ করছেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা নিয়ে, ফলিত গণিত নিয়ে, আবার পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানেও হাত দিয়েছেন। আপনার মতে, তাত্ত্বিক বিজ্ঞানচর্চা আর পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানচর্চা, এই দুইয়ের মধ্যে কি একটা স্পষ্ট সীমারেখা আছে?
আমার মনে হয়, বিজ্ঞানীসমাজের কথা ভাবলে, বিংশ শতাব্দী থেকে, এরকম একটা সীমারেখা টানার রেওয়াজ আছে। গোটা বিজ্ঞানের ইতিহাস দেখলে রেওয়াজটা কিন্তু বেশিদিনের নয়। তার আগে, যারা বিজ্ঞানী ছিলেন বা প্রাকৃতিক দার্শনিক (natural philosophers) ছিলেন, তারা এই তত্ত্ব আর পরীক্ষার বিভেদটা করতেন না।
আমার মতে, পরীক্ষামূলক গবেষণাতে, চারিদিকের পৃথিবীতে যে নকশাগুলো (patterns) দেখছি, সেগুলোকে সুনিশ্চিতভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়। আর তাত্ত্বিক গবেষণাতে এই নকশাগুলোকেই খাতায়কলমে পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করা হয়। একভাবে ভাবলে, মনের মধ্যে নকশাগুলোকে ধরার চেষ্টা করা হয়। এখন আমি যদি মনের মধ্যে নকশাগুলোকে ধরার চেষ্টা করি, তাহলে আগে বাইরের পৃথিবীতে যা দেখছি, তাকে এমনভাবে বর্ণনা করতে হবে যাতে সেটা পুনরাবৃত্তি করা যায়। তাই, প্রায় সবসময়েই তত্ত্বের আগে পরীক্ষা আসে।
অবশ্যই, কয়েকবার এরকমও হয়েছে যে তত্ত্ব আগে এসেছে। এই ঘটনাটা বিরল, কিন্তু কয়েকবার ঘটেছে এরকম। কিন্তু সাধারণত, বিশেষ করে আমি যেসব বিষয় নিয়ে জানি, যেসব সমস্যা নিয়ে কাজ করেছি, সেখানে তত্ত্ব আর পরীক্ষা প্রায় একসাথেই এগিয়েছে। কখনো, তত্ত্ব একটু এগিয়ে, কখনো পরীক্ষা। কে এগিয়ে সেই নিয়ে আমি খুব একটা মাথা ঘামাই না। গবেষণার ফল ঘোষণা করার সময় এলে যদি তত্ত্ব-পরীক্ষা দুটোই থাকে, তাহলেই চলবে।
সাধারণত, আমরা যখন কোনো ঘটনাকে বোঝার চেষ্টা করি এবং ঘটনার আড়ালে সূত্রের খোঁজ করি, আমরা শুরু করি একটা অনুমান (hypothesis) দিয়ে। তারপর কিছু পরীক্ষা (experiments) করি, সেখান থেকে তথ্য পাই কিছু। তথ্যগুলো অনুমানের সাথে মিলে গেলে বলি, এই একটা সূত্র পাওয়া গেল (যেমন, একটা পদার্থবিদ্যার সূত্র)। কিন্তু বিশ্বের কিছু জায়গায়, যেমন ভারতে, এই পরীক্ষা করার ব্যাপারটাকে খুব হ্যালফ্যালা করা হয়। এটা নিয়ে আপনার কী মত?
পরীক্ষা করার ব্যাপারটা যে হ্যালাফ্যালা করা হয় বা তেমনভাবে শেখানো হয়না, এর কারণ হয়তো এই যে পরীক্ষার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট নয় সবার কাছে। অনেকসময়, পরীক্ষা করাকে জটিল সরঞ্জামের ব্যবহার হিসেবে ভাবা হয়। আসলে জটিল সরঞ্জামের পরিবর্তে চাই জটিল চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা। কিন্তু সেইটা না থাকলে মনে হতে পারে সরঞ্জামের অভাবে জটিল পরীক্ষাগুলো করা সম্ভবই নয়। যেমন, কোয়ান্টাম হল এফেক্ট (quantum Hall effect) মাপা সোজা নয় (যদিও আমাদের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্তরে ছাত্ররা এখন এটা শেখে)।
কিন্তু মাপার সরঞ্জাম জোগাড় করতে না পারলে একটা বিকল্প রয়েছে। পৃথিবীটাকেই পর্যবেক্ষণের জায়গা হিসেবে বেছে নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এখন সারা বিশ্বে, ভারতে সর্বত্র না হলেও অনেক জায়গাতেই, যুবকদের হাতে স্মার্টফোন আছে। নিজের না থাকলেও হয়তো গোটা পরিবারে একটা আছে। এমনিতে এগুলো যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হয় কিন্তু এগুলোকে বিভিন্ন জিনিস মাপার যন্ত্র হিসেবেও ভাবা যেতে পারে। শব্দ মাপতে পারো, আলো মাপতে পারো — ভিডিওর কথা বলছি — ছবি নিতে পারো যেরকম খুশী। কিন্তু শুধু নিজের বা একে অপরের ছবি না তুলে চারিপাশের বিশ্বের ছবি তুলতে পারো। আমার অনেক সহকর্মী আছে যারা এরকম app বানিয়েছে যাতে একটা iPhone কি Android phone কি অন্য যেকোনো স্মার্টফোনকে একটা সেন্সর (sensor) হিসেবে ব্যবহার করা যায়, পৃথিবীটাকে আরো উন্নত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখা যায়।
মাপার সরঞ্জাম জোগাড় করতে না পারলে একটা বিকল্প রয়েছে। পৃথিবীটাকেই পর্যবেক্ষণের জায়গা হিসেবে বেছে নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যায়।
ব্যাপারটা শুনে যতটা কঠিন লাগছে, ততটাও কিন্তু নয়। আমার মনে হয়, ছোটদের মধ্যে একটা সহজাত কৌতূহল রয়েছে এবং ওদের হাতে এই ধরণের যন্ত্র তুলে দিলে ওরা সেটা নিয়ে অনেকদূর যেতে পারবে। একটু পথ দেখিয়ে দিলে একসময় ওদের সামনে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য ভেসে উঠবে। সেই সাদৃশ্যকে হয়তো তক্ষুণি তারা অঙ্কের ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না কিন্তু সেসব পরে হবে। আমার মতে, শিশুদের মধ্যে জানার যে আগ্রহ রয়েছে, সেটাকে একটু উস্কে দেওয়াই হবে আমাদের কাজ। যতক্ষণ না অব্দি তারা সেই আগ্রহটাকে নিয়ে কী করতে চায় সেটা নিজেরাই বুঝতে পারে, ততক্ষণ অব্দি আমাদের সেটা আগলে রাখতে হবে, টিকিয়ে রাখতে হবে।
আমি কিন্তু এইটা আশা করছি না যে সব্বাই বিজ্ঞানী হবে। শুধু এইটুকু আশা করি যে সবাই বুঝতে পারবে যে চারিপাশের পৃথিবীটাকে চাইলে বোঝা যায়। আমার কাছে, বিজ্ঞানের মূল কথা সেটাই — পৃথিবীটাকে যে বোঝা সম্ভব, বিজ্ঞান সেইটা আমাদের দেখিয়ে দেয়। কুসংস্কার কি অন্ধ বিশ্বাসে আটকে থাকার প্রয়োজন নেই। যেভাবে ভাবা হয়ে আসছে, সেটাকেই অনুসরণ করে চলার প্রয়োজন নেই। যেটা বললাম আগে, বিজ্ঞান মূলত একটা পথ দেখিয়ে দেয় কীভাবে জানা-অজানার পরিধিটার মাঝে নিজেকে পরিচালনা করা যায়। যেটা জানি, সেটা কেন জানি আর যেটা জানি না, সেটা কীভাবে জানা যায়, তার কিছু উপায় আমাদের সে শিখিয়ে দেয়।
আমার কাছে, বিজ্ঞানের মূল কথা সেটাই — পৃথিবীটাকে যে বোঝা সম্ভব, বিজ্ঞান সেইটা আমাদের দেখিয়ে দেয়।
একদম সহমত। খুব গভীর কথা বলেছেন। এখান থেকে একটা অন্য ধরণের প্রশ্ন আসছে। ইতিহাস ঘাঁটলে পশ্চিমী বিজ্ঞান আর ভারতীয় প্রাচীন বিজ্ঞানের মধ্যে একটা তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমী বিজ্ঞান বরাবরই পদার্থের সাথে পদার্থের ক্রিয়া নিয়ে ভেবেছে। অন্যদিকে, পদার্থের সাথে আমাদের মনের কিরকম আন্তঃক্রিয়া হয়, ভারতীয় বিজ্ঞানে তার উপর অনেকটা জোর দেওয়া হয়েছে। আপনার কি মনে হয়, এই দুটো পথ কি একই প্রকৃতিকে বোঝার দুটো ভিন্ন পথ নাকি পথদুটো কোথাও গিয়ে মিলছে?
এইটা খুব কঠিন প্রশ্ন। আমার মনে হয়, পদার্থের সাথে মনের ক্রিয়া, এই বিষয়টা পদার্থের সাথে পদার্থের ক্রিয়া বা পদার্থের মধ্যে কী ঘটছে, সেইটা বোঝার থেকে অনেক কঠিন। বিজ্ঞান আজকে কিছুটা সফল এই কারণেও যে সমস্যা বাছার সময় বিজ্ঞানীরা কিছুটা সুবিবেচনা দেখিয়েছেন। এর জন্য আমাদের আগের বিজ্ঞানীদের কাছে আমরা ঋণী। তারা শুধু এটাই দেখাননি যে কীভাবে সমস্যার সমাধান করতে হয়, তারা এটাও দেখিয়েছেন যে কোন সমস্যায়গুলোকে নিয়ে আগে ভাবা উচিত।
কিন্তু বিজ্ঞানে উচ্চাকাঙ্ক্ষার তো অভাব নেই। যত আমরা জড় পদার্থের মধ্যে ক্রিয়াগুলো বুঝতে পারছি, তত সজীব পদার্থ নিয়ে প্রশ্ন করার স্পর্ধাও বেড়ে যাচ্ছে। সজীব পদার্থের আচরণ আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে চেষ্টা করছি আমাদের গবেষণায়। গবেষণাগুলো হতে পারে একেকটা ব্যাকটেরিয়ার আচরণ নিয়ে, হতে পারে একদল মানুষের আচরণ নিয়ে কিম্বা হতেও পারে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট যন্ত্রমানবের মধ্যে সেই আচরণকে ধরার চেষ্টা।
তুমি জিজ্ঞেস করছো এই পথগুলো ভিন্ন নাকি কোথাও গিয়ে মিলছে। আমার মনে হয়, পথগুলোকে আলাদা দুটো পথ ভাবার দরকার নেই। দুটো পথেই ক্রমশ একটা ধোঁয়াশা কাটাবার ব্যাপার রয়েছে। দুটো পথেই আমরা প্রশ্ন করে চলেছি, এমন প্রশ্ন যার একটা উত্তর থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পুরোটা না জানলেও কিছুটা জানার সম্ভাবনা রয়েছে।
কি জানো, উত্তর পাওয়া সম্ভব কিনা, সেই বাধ্যবাধকতা দর্শন বা দার্শনিকদের নেই। তাঁরা গভীর প্রশ্ন করেন সবসময় উত্তর পাওয়ার আশা না করে। অন্তত অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তর পাবেন, এই আশা না করে। বিজ্ঞান একসময় এখান থেকেই শুরু হয়েছিল এবং এটা নিছক কোনো দুর্ঘটনা নয়। আজকে যেটাকে বিজ্ঞান বলি, কথাটা উইলিয়াম উইওয়েল-এর দেওয়া, এটাকে একসময় প্রাকৃতিক দর্শন বলা হতো। অর্থাৎ, তার এক্তিয়ারের মধ্যে ছিল বাইরের প্রকৃতি, যেটা মানবমন সৃষ্ট দর্শনের থেকে একটু আলাদা।
অতএব, আমরা ধারণা, এই দুটো পথ একে অপরের সাথে যুক্ত। এগুলো ভিন্ন পথ নয়, তবে কোথায় গিয়ে মিলবে, সেটা বুঝতে এখনো অনেক দেরি আছে।
এরকম কি বলা যায় যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর মাধ্যমে দুটোর মধ্যে যোগসূত্র পাওয়া যায়? পর্যবেক্ষণের কারণে ফলাফল পাল্টে যেতে পারে, এই ধরণের কথা বলার সময় শ্রোয়েডিঙ্গার-এর মত প্রতিষ্ঠাতা-গোত্রের লোকেরা বোধহয় বস্তু আর চেতনার যোগসূত্র নিয়ে ভেবেছিলেন। আপনার এই নিয়ে কী মনে হয়?
এই নিয়ে আমার খুব একটা ধারণা নেই। পর্যবেক্ষণের কারণে যে ফলাফল পাল্টে যেতে পারে, সেটা যদিও কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এ প্রথম অঙ্কের ভাষায় বলা হয়েছিল, ধারণাটা কিন্ত তার আগে থেকেই ছিল। তুমি এটা অন্যত্রও দেখতে পাবে, সম্পূর্ণ সনাতন সিস্টেম-এ, খুব বড় স্কেল-এ দেখলে।
জানি না প্রশ্নটা নিয়ে কোনদিকে যাওয়ার চেষ্টা করছো। কোয়ান্টাম মেকানিক্স চেতনাকে বোঝার একটা উপায় হতে পারে কি না, এরকম জিজ্ঞেস করছো কি? জানি না। যখন চেতনা, বোধ, এইসব নিয়ে প্রশ্ন আসে, আমরা সত্যিই জানি না। কী হতে পারে মনে হয়? সেটা একটু বলতে পারি। আমাদের মনে হয়, চেতনা ইত্যাদি অনেকগুলো জীবন্ত সত্ত্বার মধ্যে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া থেকে আসে। এই সত্ত্বাগুলো হতে পারে স্নায়ু (neuron), হতে পারে কোনো জীব, হতে পারে একটা জীবের কলোনি কি বাস্তুতন্ত্র। আস্তে আস্তে এরকম একটা ধারণা তৈরী হচ্ছে যে বস্তু আর চেতনার মধ্যে যোগসূত্র, কি চেতনা কোত্থেকে আসে সেই প্রশ্ন, এগুলোর উত্তর অনেকগুলো আন্তঃক্রিয়ার যৌথ ফল (collective nature of interactions) হিসেবে ধরা দেবে। এটা কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স যেভাবে শুরু হয়েছিল, তার থেকে অনেকটাই আলাদা। কোয়ান্টাম মেকানিক্স কিন্তু শুরুর দিকে খুব সহজ সিস্টেম-এই সীমিত ছিল।

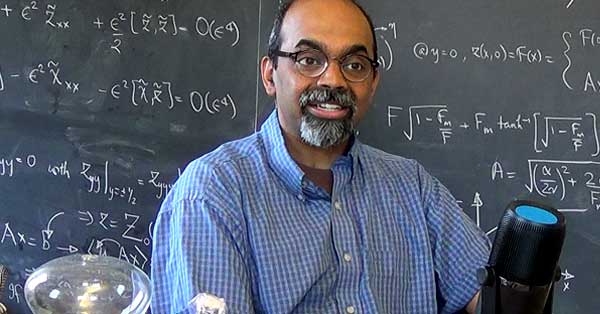
Kaushik,
Lekha ta khub bhalo laglo. Pathak er bistriti baranor jonno er songe English version tao add kora jete parto. If possible please consider.