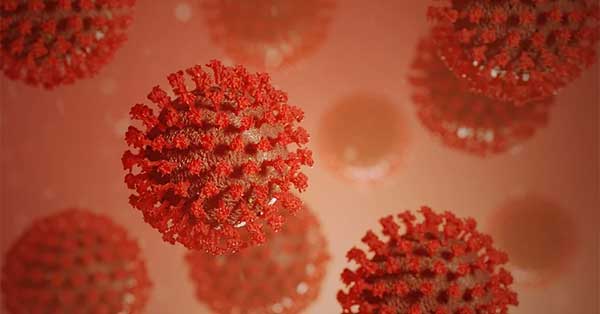করোনাভাইরাস SARS-CoV‑2 এবং তার থেকে জাত কোভিড-১৯, এখনো এদের প্রভাব সম্পূর্ণ বোঝা যায়নি। একদল লোক নিজের অজান্তেই ভাইরাস বয়ে বেড়ায়, অপরদিকে অন্য একদল ভাইরাসের কবলে পড়লো তো আর রক্ষে নেই। ভারত আস্তে আস্তে যত স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফেরত আসার চেষ্টা করছে, ভাইরাসও তেমনি ছড়াচ্ছে আরো প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা তুলনায় দুর্বল। তাই বোঝা দরকার ভাইরাসের ছোঁয়াচ কিভাবে লাগে এবং কাদের বেশি সুরক্ষার প্রয়োজন।
এই দুটো প্রশ্নেরই একটা চটজলদি উত্তর আছে। তাদেরই বেশি সুরক্ষার প্রয়োজন যাদের মধ্যে কোভিড-১৯-এর উপসর্গগুলো বেশিমাত্রায় দেখা যায়, প্রায়শই যাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দরকার পড়ে। অন্যদিকে ছোঁয়াচের সম্ভাবনা তাদের থেকেই বেশি যাদের মধ্যে সেই উপসর্গগুলো একেবারেই নেই, তাই তাদের চেনার উপায় নেই। এই উত্তর থেকে কোভিড-১৯ সামলানোর যে উপায়টা বেরোয় সেটা খুব সহজ: যত বেশি রোগ সনাক্ত করা যাবে, তত সুবিধে হবে সামলাতে। যদি এই ভাইরাসকে অল্প খরচে চেনার উপায় থাকতো, যেটা বাড়িতে কিনে রাখা যেত, যেমন সুগার বা প্রেসার মাপার যন্ত্র কিনে রাখা যায়, তাহলে কোভিড-১৯-এর ছবিটা হয়তো এদ্দিনে অন্যরকম হতো। কিন্তু সেসব না থাকায় আমাদের ভাইরাস সনাক্তকরণের জন্য বিভিন্ন রকমের উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। প্রত্যেকটা উপায়েরই কিছু ভালোখারাপ দিক রয়েছে।
একটা ভাইরাস চেনা যায় কিভাবে?
ভাইরাসের মতো অতিক্ষুদ্র জিনিস খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। একটা উপায় হতে পারে পরোক্ষ সনাক্তকরণ। ভাইরাস থাকলে যে উপসর্গগুলো দেখা যায়, তাই থেকে তাকে চেনা সম্ভব। কিন্তু কোভিড-১৯-এর উপসর্গ বিভিন্ন রকমের। তার মধ্যে কিছু যেমন কাশি কিম্বা জ্বর সার্স-কভ-২-এর (SARS-CoV-2) একার বিশেষত্ব নয়। অনেকরকম ভাইরাসের আক্রমণেই সেগুলো দেখা যায়। তাই, বাইরের উপসর্গের উপর ভরসা না করে রোগীর স্যাম্পল-এ মলিকুলার বায়োলজি-র নানা পদ্ধতিতে ভাইরাস-এর টুকরো খোঁজা হয়। এই টুকরোগুলো হতে পারে ভাইরাসের প্রোটিন বা জিনোম-এর অংশ, যেমন রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (আরএনএ)। এগুলো পাওয়া যায় নাসিকা কিম্বা গলা থেকে নেওয়া swab কিম্বা থুতুর স্যাম্পল-এ। তুলনায় কম হলেও কিছু রোগীর মলে ভাইরাসের আরএনএ পাওয়া যায়।
বহিরাগত বস্তুর সংক্রমণ হলে আমাদের দেহ প্রত্যুত্তরে অ্যান্টিবডি তৈরী করে। দেহের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা (immune system) সেই বস্তুর প্রোটিনের অংশবিশেষ থেকে বুঝতে পারে, এ জিনিস এখানকার নয়, এদের এখানে থাকলে চলবে না। সেই চিনিয়ে দেওয়া প্রোটিনগুলোকে বলে অ্যান্টিজেন। এদের উত্তরে দেহও তৈরী করে নিজের একদল প্রোটিন, যেগুলো সেই অ্যান্টিজেন-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এই প্রোটিনগুলোকেই বলে অ্যান্টিবডি। এদের তৈরী করে রক্তে ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে, রক্তপরীক্ষা করে কোনো বিশেষ অ্যান্টিবডি কিম্বা অ্যান্টিজেন খুঁজে পেলে তার থেকে সংশ্লিষ্ট ভাইরাসের উপস্থিতি টের পাওয়া যেতে পারে।
RT-PCR – ভাইরাস চেনার সর্বস্বীকৃত পদ্ধতি
ভাইরাসের আরএনএ ক্রমবিন্যাস (RNA sequence) ২০২০-র ফেব্রুয়ারীতেই হাসিল হয়ে গেছিল। এর ফলে গবেষকরা সেই বিন্যাসের বিশেষ কিছু জায়গাকে ভাইরাসের ‘দস্তখত’ হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলোকে খোঁজার পদ্ধতি বার করে ফেললেন। Reverse Transcriptase – Polymerase Chain Reaction বা সংক্ষেপে RT-PCR পদ্ধতিতে উৎসেচকের মাধ্যমে এই বিশেষ জায়গাগুলোকে সংখ্যায় বাড়িয়ে তারপর সেগুলোকে সনাক্ত করা হয়। এই পদ্ধতির সাফল্যের হার ৭০ শতাংশ। অর্থাৎ ১০০-টা ভাইরাস-আক্রান্ত স্যাম্পলের মধ্যে ৩০-টা ধরা নাও পড়তে পারে। এছাড়াও এই পদ্ধতিটার জন্য চাই বিশেষ PCR মেশিন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেশিনচালক এবং মূলত বাইরে থেকে আমদানি করা রিঅ্যাকশন কিট (reaction kit)। এই সবই যোগ হয় শেষের হিসেবে। যেহেতু স্যাম্পলে জীবন্ত ভাইরাস রয়েছে, সেগুলোকে যেখানে সেখানে পরীক্ষা করা যায়না। বিশেষ সুরক্ষাব্যবস্থা থাকলে –বায়োসেফটি লেভেল ২ (Biosafety Level 2) বা তার উপরে– তবেই একটা জায়গায় এই পরীক্ষার অনুমতি পাওয়া যায়। এসবই শ্রম এবং খরচ সাপেক্ষ। তাই অনেক লোককে অল্পখরচে পরীক্ষা করার জন্য RT-PCR মোটেই সুবিধের নয়।

অ্যান্টিবডি বা অ্যান্টিজেন-এর খোঁজ
গণহারে পরীক্ষা তখনই সম্ভব যখন সেই পরীক্ষা করতে যৎসামান্য পরিকাঠামো বা প্রশিক্ষণ থাকলেই চলবে এবং যথাসম্ভব অল্পখরচে চটজলদি করা যাবে। এই ধরণের পরীক্ষার সময়োত্তীর্ণ উপায় হলো অ্যান্টিবডি বা অ্যান্টিজেন-এর খোঁজ করা। অ্যান্টিবডি যেহেতু তার জুড়িদার অ্যান্টিজেন-এর সাথেই বন্ধন স্থাপন করতে পারে, একগুচ্ছ অ্যান্টিবডি স্টকে থাকলে রক্তের স্যাম্পলে অ্যান্টিজেন-এর উপস্থিতি সনাক্ত করা যায়। বা উল্টোটা, অর্থাৎ অ্যান্টিজেন-এর সাহায্যে অ্যান্টিবডির সনাক্তকরণ, সেটাও করা যায়। অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি দুটোকেই ব্যাপক হারে তৈরী করা, আলাদা করা এবং শুদ্ধিকরণ করা সম্ভব। বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেলে এদের একটা প্লেট কি কাগজের স্ট্রিপে বন্দী করে যেখানে প্রয়োজন সেখানে ব্যবহার করা যায়। অ্যান্টিজেন-এর সাথে যে অ্যান্টিবডির বন্ধন ঘটলো, সেটা সাব্যস্ত করা যায় নানাভাবে, এবং এই ধরণের পরীক্ষা ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন রোগ সনাক্ত করা হয়েওছে। শুনতে সোজা লাগলেও একটা নতুন অ্যান্টিবডি বা অ্যান্টিজেন টেস্টিং কিট বানাতে কিছু ধকল রয়েছে। সার্স-কভ-২ ভাইরাসটার অ্যান্টিজেন টেস্টিং কিট বানাতে প্রথমে শুধু এই ভাইরাসেই প্রকাশ পায়, এরকম অ্যান্টিজেন চিহ্নিত করতে হবে। সেই অ্যান্টিজেন-এর অ্যান্টিবডি তৈরী করে জমাতে হবে ভবিষ্যতের পরীক্ষার জন্য। তার জন্য একটা শর্ত হলো, অ্যান্টিজেনটাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হতে হবে যাতে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার কাছে সেটা ধরা পড়ে। কেন? কারণ অ্যান্টিবডিটা সৃষ্টি করা হয় গবেষণাগারের ইঁদুর-প্রভৃতি জন্তুর শরীরে (সবরকম অনুমতি নিয়ে)। তারপর তাকে আলাদা করে তবেই অ্যান্টিজেন টেস্টিং কিট-এ ব্যবহার করা হয়।

অ্যান্টিবডি টেস্টিং কিট বানাতে গবেষণাগারে তৈরী কোষের ভিতর সার্স-কভ-২-এ পাওয়া যায়, এরকম অ্যান্টিজেন বানানো হয়। এভাবে কৃত্রিম উপায়ে প্রচুর অ্যান্টিজেন বানানো গেলেও সেই অ্যান্টিজেন-এর সহজাত গঠনের সাথে এদের কিছু তফাৎ থেকে যায়। তাই, সেই অ্যান্টিজেন আমাদের দেহের ভিতর তৈরী অ্যান্টিবডির সাথে বন্ধন স্থাপন করবে কিনা, তার নিশ্চিত গ্যারান্টি নেই। এছাড়া, স্যাম্পলে ভাইরাসের সংখ্যা কম থাকলে, যেমন ছোঁয়াচ লাগার শুরুর দিকে, অ্যান্টিবডি টেস্টিং-এ ধরা নাও পড়তে পারে। তাই, এই পরীক্ষায় নেগেটিভ রেজাল্ট এলেও RT-PCR-এর মাধ্যমে সেই রেজাল্ট যাচাই করে নেওয়া উচিত। ওটাই এখনো অব্দি সবথেকে নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা।
অ্যান্টিবডি টেস্টিং কিট-এর আরেকটা সমস্যা হলো, যতই সার্স-কভ-২-এর জন্য ডিজাইন করা হোক না কেন, সে অন্য ধরণের করোনাভাইরাসের অ্যান্টিবডিকেও চিহ্নিত করে ফেলতে পারে। অপরদিকে, উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর দেহে অ্যান্টিবডির জন্ম হতে সপ্তাদুয়েক লাগে। তাই তার মধ্যে পরীক্ষাটা করলে পজিটিভ ধরাই পড়লো না, এমনও হতে পারে। আনুমানিক ১০ শতাংশ আক্রান্ত ব্যক্তি এই পরীক্ষায় পজিটিভ ধরা পড়ে না। আমরা এটাও নিশ্চিতভাবে জানি না যে দেহে অ্যান্টিবডি জন্মানোর পর সেটা কতদিন অব্দি থাকে। তার মানে অ্যান্টিবডি টেস্টিং করে একটা অঞ্চলের কতজন আক্রান্ত, তার সঠিক ছবি পাওয়া গেল কিনা, সেটাও আমাদের কাছে এখনো স্পষ্ট নয়।
সার্স-কভ-২-এর স্পাইক (S) এবং নিউক্লিওক্যাপসিড (N) প্রোটিন এইসব পরীক্ষার কিট বানাতে অ্যান্টিজেন হিসেবে ব্যবহারের জন্য আদর্শ। বিশেষ করে N প্রোটিন এই ভাইরাসে সবথেকে বেশি রয়েছে এবং ফলে সহজেই অ্যান্টিবডির জন্ম দেয়। যদিও S প্রোটিন ব্যবহার করলে আরো ভালো কারণ এই প্রোটিনটা সার্স-কভ-২-কে অন্যান্য করোনাভাইরাসের থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়।
জনগণের উপর নজর রাখার উপায়
এখন বাজারহাট, দোকানপত্তর সব খুলে গেছে। তাই, কোথাও সংক্রমণ বাড়ছে কিনা, সেটা নজর রাখার একটা সহজ উপায় থাকলে ভালো। লোকের ঘরে ঘরে গিয়ে পরীক্ষা করার উপর নির্ভরশীল না হয়ে অন্য কোনো উপায়ে এই নজরদারি করতে পারা জরুরি। বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে যেখানে অনেকগুলো অঞ্চলে জনসংখ্যা ঘনত্বের কারণে এইধরণের ঘরে-ঘরে পরীক্ষা প্রায় সাধ্যের বাইরে।
মুম্বাই, দিল্লী, পুনে এবং অন্যান্য অনেক শহরে এখনো অব্দি এইরকম পরীক্ষা হয়েছে। কিছু অঞ্চলে ঘরে-ঘরে রক্তের স্যাম্পল নিয়ে পরীক্ষা করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে পুরো শহরটার একটা ছবি তৈরী করার চেষ্টা হয়েছে। গোটা দেশেই এখন এরকমভাবে নজর রাখার চেষ্টা চলছে। এইসব পরীক্ষার উপর নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার যাচাই করতে পারে তাদের কোভিড সামলানোর নিয়মকানুনগুলো কাজে দিলো কিনা। কিন্তু এইভাবে নজর রাখতে হলে অনেক স্বেচ্ছাসেবক লাগবে। সংক্রমণের উপর নজর রাখার এমন উপায়ও হয় যাতে স্বেচ্ছাসেবক লাগে না এবং লোককে ধরে ধরে পরীক্ষাও করতে হয়না। আক্রান্ত ব্যক্তি মূলত নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে বাতাসে কিম্বা জলে যেসব ভাইরাস ছেড়ে যায়, সেগুলোকে সনাক্ত করেও এই কাজটি করা যায়। তবে বাতাসের মাধ্যমে নজরদারির উপায় নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে। আরেকটা উপায় হলো নিকাশী পদার্থের (sewage) উপর নজর রাখা। কোভিড আক্রান্ত রোগীদের ৩০ থেকে ৬০ শতাংশের মলের মধ্যে ভাইরাসের আরএনএ থাকে, ফলে নিকাশী পদার্থে তাদের উপস্থিতি সনাক্ত করা যায়। চেন্নাই বা হায়দরাবাদ-এ এরকম নিকাশী পদার্থের উপর নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে এইসব পদার্থগুলোকে রাসায়নিকভাবে সংস্কার করা হয়, সেইসব সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এ কতটা পদার্থ এলো, কোত্থেকে এলো সেসবের হিসেব থাকে। নিকাশী জলে কতটা ভাইরাস-এর আরএনএ রয়েছে, সেটা RT-PCR পদ্ধতিতে মাপা যায়। দুইয়ে মিলে গবেষকরা একটা পরোক্ষ ধারণা করতে পারেন শহরের কোথায় কতটা সংক্রমণ হয়েছে।

উপসর্গ দেখা দেওয়ার প্রায় ৩৫ দিন পর অব্দি রোগীর মলে সার্স-কভ-২ ভাইরাসের আরএনএ থাকতে পারে। অতএব এইরকম নিকাশী পদার্থের উপর পরীক্ষা করলে যে কোনো একটা অঞ্চলে গত এক মাস কি অবস্থা ছিল, তার একটা মোটামুটি ছবি পাওয়া যায়।
এতসব জেনে কি হবে?
এইরকম বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাওয়া ফলাফলগুলোকে নিয়ে সরাসরি একে অপরের সাথে মেলানো ঠিক নয়। হায়দরাবাদে যখন নিকাশী পদার্থের পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া ফলাফল ঘোষণা করা হলো, তখন হইচই পড়ে গেছিল। হঠাৎ সংক্রমণ বেড়ে গেল কি করে? যেটা লক্ষ্য করা হয়নি সেটা হলো যে প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ পরীক্ষার মধ্যে তফাৎ রয়েছে। দ্বিতীয়টাতে অনেক বেশী লোককে পরীক্ষার আওতায় আনা যায়।
নিকাশী পদার্থ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনেক বড় এলাকা জুড়ে সংক্রমণের চেহারাটা যথাসামান্য কম খরচে পাওয়া যায়। কিন্তু এই পদ্ধতিটা মূলত শহুরে অঞ্চলেই সীমিত। অন্যদিকে, বেশীরভাগ স্বাস্থ্যকর্মীই রক্তে অ্যান্টিবডির মাধ্যমে রোগনির্ণয়ে অভ্যস্ত। এটা অবশ্যই শহর গ্রাম দুজায়গাতেই চালু আছে। রক্তপরীক্ষার ফলাফলের তথ্যে খুব নিখুঁতভাবে খেয়াল রাখা যায় রোগীদের বয়েস কত, তাদের মধ্যে স্ত্রী কতজন আর পুরুষ কতজন, বা তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা কিরকম। সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া যায় একটা বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে রোগের প্রকোপ কমাতে। কিন্তু এই ধরণের পরীক্ষার ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগে খেয়াল রাখা উচিত যে কাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে, সেই গোড়ার প্রশ্নটাতেই একটা পক্ষপাত থাকতে পারে। যেমন, মুম্বাইতে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল সেখানে মহিলাদের কম আক্রান্ত মনে হয়েছিল কারণ মহিলাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণই ছিল কম।
এত ধরণের পরীক্ষা হচ্ছে যে তাদের ভিত্তিতে পাওয়া রোজকার খবর শুনে ঘেঁটে যাওয়া স্বাভাবিক। কি ধরণের পরীক্ষা এবং তথ্যসংগ্রহ হচ্ছে, সেটা অনেকাংশেই সে অঞ্চলে কি যন্ত্রপাতি বা প্রশিক্ষণ রয়েছে, তার উপর নির্ভর করে। এইসব পরীক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে শুধু ব্যক্তিস্বাস্থ্য নিয়ে মাথা ঘামানো বা হতে পারে একটা গোটা এলাকায় সংক্রমণ ঠেকানো। যেহেতু একেকটা পদ্ধতি একেকরকম সূক্ষ্মভাবে রোগ চিহ্নিত করতে পারে, তাই তাদের ভিত্তিতে পাওয়া সংক্রমণের ছবিটাও আলাদা হতে পারে। এই লেখাটা পড়ার পর আশা করি, আগামী দিনে যদি আপনার বা আপনার অঞ্চলে কোভিড পরীক্ষা হয়, আপনি বুঝতে পারবেন ঠিক কি পরীক্ষা করা হচ্ছে, কি তার পদ্ধতি, এবং কিভাবে তার ফলাফলগুলোর পাঠোদ্ধার করা যায়।
(লেখাটি প্রথম IndiaBioscience-এ প্রকাশিত হয়েছিল। মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছে ‘বিজ্ঞান’ টীম-এর অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়।)